ভাণ পত্রিকা
৩৭ তম ই-সংস্করণ ।। ৪৭ তম সংখ্যা ।।এপ্রিল ২০২৪
সম্পাদক :

সম্পাদনা সহযোগী :

প্রচ্ছদ :

নক্সা পরিকল্পক :

অন্যান্য কাজে :








ভাণ-এর পক্ষে:
পার্থ হালদার
কর্তৃক
৮৬, সুবোধ গার্ডেন, বাঁশদ্রোণী, কলকাতা : ৭০০০৭০ থেকে প্রকাশিত। যোগাযোগ : ৯৬৪৭৪৭৯২৫৬
( হোয়াটসঅ্যাপ ) ৮৩৩৫০৩১৯৩৪ ( কথা / হোয়াটসঅ্যাপ )
৮৭৭৭৪২৪৯২৮ ( কথা ) bhaan.kolkata@gmail.com ( ই – মেল )
Reg. No : S/2L/28241
সম্পাদকের কথা
।। সম্পাদকের কথা।।
এপ্রিল, ২০২৪
গৌরাঙ্গ দণ্ডপাট
রৌদ্রক্লান্ত পথিক যেমন ছায়ার স্মৃতির ঘোরে পুড়তে পুড়তে এগিয়ে চলে, ভেসে যেতে যেতে মানুষ যেমন গাঁ-গেরামের সবুজ গাছালি আর লালচে সোনালী ধানের স্বপ্ন দেখে; অসুস্থ আর মুমূর্ষু মানুষ যেমন পাহাড় ভেঙে চূড়োয় ওঠার কল্পনায় একটিবার পাশ ফিরে শোয়, তেমনি আমরা আমাদের চারপাশের পোড়ো জমির ওপরে ক্লান্ত হাতে আবির ছড়াতে ছড়াতে ভাবি ‘রঙিন’ সময় এসে গেছে!! এ সময়ের ঘোর লাগা অভিশপ্ত পুরীতে সবাই কেবল পালাতে থাকে। দায় ছেড়ে, চোখ নামিয়ে, ঘাড় ঘুরিয়ে কেবলই পালায়। চোখটাকে খোলা রাখার মানে আদতে ঘুমায়। পালায়, অথচ পুরোটা পালাতে পারে না। মেনে নেয়, তবু মনকে মানাতে পারে না। মানুষ বাঁচে, পালিয়ে অথবা লড়ে। চিরকাল। পালিয়ে বাঁচার পাল্লা ভারী হলে আমাদের কালের মতো মুমূর্ষু হয়ে পড়ে সময়। বাতাস গ্লানির গন্ধে ভরে ওঠে।
সিনেমা পালায়। থিয়েটার পালায়। সঙ্গীত পালায়। কেউ আর সময়ের সঙ্গে ঘর করে না। কেউ আর সন্তানের হাহাকারের দায় নেয় না। কেউ আর একালের রাধার বিরহের সঙ্গী হয় না। কেউ অন্যের দিকে বাড়িয়ে দেয় না সদয়-হাত! তাহার খুশিতে আমার আনন্দ কই? পাশে দাঁড়ানো, কাছে বসা, ছুঁয়ে থাকা ক্রমশ বিরল অনুভূতি। পাশের যন্ত্রণায় কাতরতা এখন বোকামি। চালাক হতে গিয়ে পা চালিয়ে আমরা কোথায় পালাচ্ছি? শুধু কি আমরা!? আমাদের যা কিছু সৃষ্টি অথবা নির্মাণ– সন্তান সন্ততি অথবা কাব্য, চিত্র কিংবা সুর– সব পা চালিয়ে কোথায় পালাচ্ছে? কী হতে চায় সে? মহান হবে বলে? অমরত্ব পাবে বলে? মিথ্যার স্বর্গ রচবে বলে?
একটা গোটা জাতি আকন্ঠ দুর্নীতির পাঁকে তলিয়ে যাচ্ছে, থিয়েটারে সে কথা নেই। সিনেমায় সে উদ্বেগ নেই। সঙ্গীতে নেই সে বিষাদ অথবা ক্ষোভ। বাঙালির রাজনীতির ভাব ভাষা নীতি নৈতিকতা চুলোয় যাচ্ছে। আমরা সিনেমাতে গোয়েন্দা থ্রিলার সাইকির বিচিত্র খেলা দেখছি। উত্তমকুমার কথা বলছেন, সুপ্রিয়া দেবী চোখ মারছেন–জাতীয় রগড় চাখছি। চতুর্থ শ্রেণির ম্যাজিক দেখছি। কেউ দায় নেয় না। সবাই পালায়। সবাই লুকায়। কলেজস্ট্রিট-এর বই উৎপাদনের কারখানায় কেবলই গোয়েন্দা, তন্ত্র, যৌনতা, তৃতীয় শ্রেণির সেলিব্রেটির চতুর্থ শ্রেণির জীবনী, আর ঈর্ষা জর্জর মানুষের দাবিতে ভক্তির থ্রিলার!
থিয়েটার বিপ্লবের নামে কেবল অতীতচারী হয়। দূরের নিশ্চিন্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে শোভা দেখায়। যা কিছু আজকের, যে রক্ত এখনকার, যে ঘামে ভেজে বেঁচে থাকা জনতার শরীর, সে সব থেকে পাশ কাটিয়ে কেবল গোলগোল, রঙচঙে হয়ে উঠতে গিয়ে পালিয়ে যায়। সত্যের উপস্থাপনার রঙিন ধোঁয়ায় প্রকৃত সত্য মিলিয়ে যায়। জিমন্যাস্টিক দেখায় এরা। ম্যাজিক দেখিয়ে বাজি জিততে চায়। মুখরোচক হয়ে ওঠে। চোখে ওপর আলোর কারসাজিতে ঝিনঝিন লাগিয়ে দেয়। শুধু মাঠে ছড়ানো বলের মতো বীভৎস বোমাকে তুলতে গিয়ে কত শিশু, কত কিশোর মরে গেল— থিয়েটার এসবের হিসেব চায় না। থিয়েটার প্রতিবাদ শানাতে গণনাট্যের রেপ্লিকা বানায়। উৎপল খানিক বাদে বাদে নব্য সাজে, বাহ্য সুরে, আপোসী বিপ্লবীদের বিপ্লবীয়ানার চিহ্ন হন। প্রতিরোধের নামে মহাভারতের গলি ঘুঁজিতে আশ্রয় নেয় নাটক। বলার কথার চাইতে বলার ভঙ্গিতে, প্রকাশের আঙ্গিকে বেশি মনোযোগ দেয়। কোন থিয়েটার, কোন সময়ের থিয়েটার– সে সব জিজ্ঞাসার চেয়ে বড় হয়, ‘আমি থিয়েটার করি’, ‘আমি থিয়েটারওয়ালা’ মার্কা বিজ্ঞাপন। অথচ ইংরাজ নেই। স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ নাকি আমাদের! দেশে নাকি গণতান্ত্রিক সরকার। তাহলে কার ভয়ে/ কোন ভয়ে পিছুটান!? কেন পালিয়ে যাওয়া? পালালে কী পায় শিল্প, কী পেতে পারে শিল্পীর জীবন? কী পেতে পারে থিয়েটার অথবা চলচ্চিত্র? কিছু না, কিচ্ছু না। তারা তাদের আকৃতি হারিয়ে প্রকৃতি খুইয়ে কেবল অবান্তর জলের আল্পনা এঁকে যেতে থাকে…
রাজনীতি মাঠের থেকে পালাচ্ছে। যুবকরা তর্ক থেকে পালাচ্ছে। সংলাপ লজিকের থেকে পালাচ্ছে। ছাত্ররা চিন্তার থেকে পালাচ্ছে। শিক্ষকরা প্রশ্নের থেকে পালাচ্ছে। ডাক্তাররা দায় থেকে পালাচ্ছে। হয়ত আমাদের দায় কেবল নিয়ন্ত্রকের কাছে। ডাক্তার অথবা শিক্ষকও আজ পুঁজির সেবক মাত্র। প্রশ্নহীন আজ্ঞাবাহী। শ্রেণি শত্রুর আদলেই আমরা কেন যে গড়ে নিতে চাইছি নিজেকে? কোন সুখের প্রত্যাশায় কে জানে!! শুধু কঠিন নয়, বড় জট পাকানো জটিল এ সময়। এই সমযনকে তো আজকের সাহসী খোঁজে ধরতে হবে! ইতি উতি বিক্ষিপ্ত সাহসের ঝিলিক থাকলেও প্রকৃত অর্থে তেমন আয়োজন আজ কোথায়!?
আমরা জায়গা ছাড়ছি না, সাজ পোশাক খুলছি না, হার স্বীকার করছি না। পালাচ্ছি তবু দেখাচ্ছি যে আমি ই তো রয়েছি! আমিই তো লড়ে যাচ্ছি!!— যে জিহ্বা থেকে এই মিথ্যাচার ঘটছে সে জিভের মালিক কি সত্যিটা জানে!? জানে কি সে পলায়নবাদী হারাধন? নাকি সে নিজের কাছেও সেকথা কবুল করে না। মানুষ আসলে নিজের থেকেই পালাচ্ছে!! ভয় পাচ্ছে। কুঁকড়ে যাচ্ছে তবু দেখাচ্ছে না। হেরে গিয়েও দাঁত কপাটে রেখে দিচ্ছে হাসি। চুরুট ফুঁকে পরিচালকের বলছেন, আপনারা বাঙলা ছবি, বাংলা থিয়েটার, বাংলা সাহিত্যের পাশে দাঁড়ান। অথচ সত্য এই, যে মানুষকে তিনি ডাকেন, তার থেকে তিনি নিজেই পালিয়েছন বহু আগে।
পালানোর পাশে একটা কথা আছে। কথাটি হল– ছেড়ে দেওয়া। ধারে ভারে একেবারে অন্য ধারার একটি কথা। কত কাছের কিন্তু কত আলাদা ভাবের একটা কথা। পালানোর পেছনে থাকে, ভয়, আশঙ্কা, নিরাপত্তাহীনতার বোধ। পালিয়েও তাকে গোপন করার মধ্যে আছে বড় করুণ এক মর্মপীড়া অথবা পাতি চালবাজি। কিন্তু ‘ছেড়ে দেওয়া, ছেড়ে আসা’– এর মধ্যে আছে সাহস। ভরপুর আত্মবিশ্বাস। বুদ্ধদেব চৈতন্য সংসার ছেড়ে এলেন, পিতৃপুরুষের লাক্সারি উত্তরাধিকার ছেড়ে এলেন বামপন্থী যুবা। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদের অবিসংবাদী দাবিদার গান্ধী কুর্শি ছেড়ে এলেন বেলেঘাটার বস্তিতে। এরা কেউ পালালেন না। লুকোলেন না। আড়াল তুললেন না।
আমরা যদি প্রতিদিন একটু একটু করে নিজস্ব চালবাজিকে ধরতে পারি। একটু একটু করে ওদের ছাড়তে পারি। তাহলে আমাদের এস্কেপিস্টের দুর্নাম ঘুচতে পারে কিছুটা। সমাজের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার ফাঁকতালে নিজের পচা কুঠুরি, নোংরা ঘুপচির আকাড়া ঘাগুলোর থেকে না পালিয়ে, না ভয় পেয়ে, চোখ বড়ো করে তাকাতে পারি কি? দাঁড়াতে পারি কি? পারি কি মোকাবিলার প্রস্তুতি নিতে?
যাপিত নাট্য ' এর বিংশ কিস্তি লিখলেন - কুন্তল মুখোপাধ্যায়

কুন্তল মুখোপাধ্যায়
১৯৯৪ সালে আমরা সংলাপ কোলকাতা হ্যারল্ড পিন্টারের “হোম কামিং” থেকে “ঘরে ফেরা” নাটকটি অভিনয় শুরু করি। ১৯৯৬-এর মধ্যে নাটকটির প্রায় ৩৮টি অভিনয় সাঙ্গ হয়। সেই সময় কলকাতার কাছাকাছি এবং দূরের শহরতলীতেও আমরা প্রচুর অভিনয় করেছি। নাটক ও নাটক সংক্রান্ত পড়াশোনা (যার উৎসমুখ অশোক মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় উন্মুক্ত করেছিলেন) আমার অভ্যাস। সেই অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে লোরেনে হ্যান্সবেরীর লেখা “রেইজিন ইন দি সান” (রোদে শুকানো কিসমিস) নাটকটির পাঠ সাঙ্গ করি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষাপটে লোরেন হ্যান্সবেরী (১৯৩০–১৯৬৫) ১৯৫৮/৫৯ সালে এই নাটকটি লেখেন। একজন ব্ল্যাক আমেরিকান লেখকের লেখা নাটক সেই প্রথম ব্রডওয়ে থিয়েটার অভিনীত হতে থাকে এবং তিনিই প্রথম একজন কালো লেখক যাঁর নাটক নিউইয়র্ক ড্রামা ক্রিটিক সার্কেল দ্বারা সম্মানিত ও পুরস্কৃত হয়। নাটকটির কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল একদল ছিন্নমূল নারী-পুরুষের জীবন সংগ্রাম, যারা গায়ের রং এর কারণে কালো মানুষ বলে চিহ্নিত। নাটকটির সামাজিক প্রেক্ষাপট, বর্ণবিদ্বেষ ও তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নাটকীয়তায় মুগ্ধ হয়ে আমি নাটকটির বঙ্গীকরণ করে ফেলি। বর্ণ বিদ্বেষের বদলে বাংলার প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় বিদ্বেষ ও বাজারী অর্থনীতির সর্বগ্রাসী লোভের বিরুদ্ধে এক পতি পরিত্যক্তা মাঝবয়সী নারী আর তার পুত্রবধূর নিত্য দিনের হার না মানা লড়াইয়ের মধ্যে স্বপ্ন দেখার বিষয়টি আমার লেখায় মৌলিক গুরুত্ব পায়। রেইজিন ইন দি সান নাটকটির শুরুতে ল্যাংস্টন হিউজের (Langston Hughes) একটি কবিতা মুদ্রিত ছিল, যার প্রথম লাইন ছিল এরকম– ‘To Mama: in gratitude for the dream’ এই লাইনটিকে মাথায় রেখেই আমি নাটকটার নাম দিলাম– স্বপ্ন নিয়ে।
স্বপ্ন নিয়ে লেখা হল, দলের ঘরে নাটকটির পাঠ হলো। দলের বাইরে আমি শ্রদ্ধেয় মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও বিভাস চক্রবর্তীর কাছে গিয়ে নাটকটি তাঁদের শোনাই ও তাঁদের পরামর্শ মত নাটকটির কিছু সম্পাদনাও করি। আমার দুই বন্ধু বিতান এবং পরিতোষ ও সুরঞ্জনার সঙ্গে (সুরঞ্জনা “ঘরে ফেরা” থেকে আমাদের সঙ্গে ছিল) পরামর্শ করে ঠিক হল মূল নাটকের “মা–মা” আমার নাটকের ‘মা’ যার নাম মহামায়ার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য আমরা মায়াদি, মায়া ঘোষকে অনুরোধ করবে। মায়া ঘোষ বলতেই আমার মনে পড়ে গেল নান্দীকারের “নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র”, থিয়েটার ওয়ার্কশপের “চাক ভাঙা মধু”, “রাজরক্ত”, “পাঁচু ও মাসী”, “বেলা অবেলার গল্প”-এর অনন্য চরিত্র রূপকার মায়া ঘোষের অভিনয়ের কথা। নাটক দেখার চল ছিল আমাদের বাড়িতে, তাই ছোটো থেকেই আমি নাটক দেখায় ও ভালোবাসায় অভ্যস্ত ছিলাম। তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেন, নীলিমা দাস, মমতা চট্টোপাধ্যায়, নিবেদিতা দাসের অভিনয় দেখেছি। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে নান্দীকার, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, বহুরূপী, এল.টি.জি/ পি.এল.টি, রূপান্তরী, সি.পি.এ.টি, থিয়েটার কমিউন, নক্ষত্র প্রভৃতি গ্রুপ থিয়েটারের নাটকের নিয়মিত নাট্যদর্শক ছিলাম। কর্মাসিয়াল মঞ্চে সরযূ বালা, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, কেতকী দত্ত, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় নাট্যভিনয়ও দেখেছি। বলতে দ্বিধা নেই ওই সময় থেকেই দুজন নারী অভিনেতার গুনমুগ্ধ ভক্ত হয়ে উঠেছিলাম। এঁদের একজন কেয়া চক্রবর্তী ও অন্যজন মায়া ঘোষ, স্কটিশ চার্চ কলেজের বন্ধুদের সূত্রে কেয়াদির সঙ্গে এক আত্মিক সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলাম। মায়াদিকে দেখেছি মঞ্চে এবং থিয়েটার ওয়ার্কশপের কিছু মহড়ায়, কী সাবলীল ভাবে সংলাপ উচ্চারণে, চরিত্র অনুযায়ী হাঁটা চলা এবং মঞ্চ ব্যবহারের উপযুক্ততায় তিনি কতটা নিখুঁত থাকার চেষ্টা করছেন। যাইহোক সাহস করে আমি আর সুরঞ্জনা একদিন সকাল সকাল মায়াদির সল্টলেকের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলাম। এর আগে আমি মনিদীপা রায় (মনিদি), নমিতা মন্ডল (নমিতাদি)দের বাড়িতে অনেকবার গিয়েছি, সীমা, সুরঞ্জনাদের বাড়িতেও প্রচুর আড্ডা দিয়েছি, কিন্তু মায়াদির ঘরে গিয়ে বিস্মিত হলাম। আভরণহীন, আড়ম্বরহীন ঘরেও যে এমন শ্রী ও আড়ম্বর থাকতে পারে, তা দেখে চমকিত হলাম, মায়াদিকে আমাদের প্রস্তাব জানালাম, উনি আমাদের “দিশা” আর “ঘরে ফেরা” দেখেছিলেন, ওঁনার ভালো লেগেছিল, সেই ভালোলাগার জায়গাটি থেকেই আমাদের দলের কাজের প্রতি ওঁনার আস্থা জন্মেছিল, আমাদের সঙ্গে কাজ করতে উনি সস্মত হলেন।
ঠিক তিন দিন পর মতিঝিলে আমার বাড়িতে বসে মায়াদি শুনলেন, “স্বপ্ন নিয়ে” নাট্যপাঠ। মূল নাটকটির বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করলেন, জানতে চাইলেন মূল নাটকটির ক্রাইসিস, এই নাটকে কীভাবে কতটা বহন করা হচ্ছে, বা কোথায় পরিবর্তন ঘটছে এবং তা স্বপ্ন নিয়ের মূল টেক্সট-এর সঙ্গে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ থাকছে। আমাদের দলের পরিতোষ দা, বিতান দা, অপু দা, প্রণব দা, দীপক, শংকর, দেবেশ এদের সঙ্গে পরিচিত হলেন, এবং এদের সকলের তাঁর সম্পর্কে প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে দিলেন, শিয়ালদহ বাণী মিন্দর স্কুলে, আমাদের মহড়া কক্ষে নাটকটির স্ক্রিপ্ট রিডিং হতে লাগল। এর পরই আমরা চলে এলাম ইছাপুর পি.এইচ.ই.র বাংলোয়– তিন দিনের আবাসিক ক্যাম্প রিহার্সাল। প্রণবদা আমাদের তৎকালীন সম্পাদকের দৌলতে আমরা ওই ক্যাম্পাসটায় এমন আবাসিক রিহার্সাল এর আয়োজন করেছি দীর্ঘকাল। মায়াদিকে “স্বপ্ন নিয়ে” তে অভিনয় করানো সময় প্রথমেই যে বিষয়টি খেয়াল রাখতাম তা হলো মহামায়া যেন বেলা-অবেলার মা না হয়ে যায়। শেকস্পীয়রের হ্যামলেট নাটকে হ্যামলেট এলসিনোরে আগত নাটকের দলকে নির্দেশ দিয়েছেন– “Suit the dialogue to the action and action to the dialogue”– প্রথম দিন থেকেই মায়াদি এই পদ্ধতিটি সহজ ভাবেই স্ব-বসে এনে সংলাপ উচ্চারণ করতে থাকলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে মায়াদি প্রথমেই আমার কাছ থেকে চরিত্রটির বয়স, তার সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে জেনে নিলেন, খুব কম অভিনেত্রীকে আমি প্রথমেই এমনটা করতে দেখেছি। মহামায়া চরিত্রটির সৃজন লেখনীতে আমি আমার পিতামহীর চরিত্রের অদল রেখেছিলাম, বিশেষ করে আমার পিতামহের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে রেখে সংসার ত্যাগের কাহিনীটি মায়াদিকে শুনিয়েছিলাম। বাহ্যিক প্রকাশে নিরাসক্ত কিন্তু অন্তরে স্নেহ-মায়ার নিগড়ে গড়া আমার পিতামহীকেই মহামায়া চরিত্রের মডেল ভেবে তৈরি হয়েছিলেন মায়াদি। অভিনয়ের সময় মায়াদি নিছক নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন না, সহ অভিনেতাদের কথাও ভাবতেন। পরিতোষদা বা অপুদার মুখে শুনেছি অভিনয় করতে করতেই মায়াদি লক্ষ রাখতেন যে তাঁর সহঅভিনেতারা যেন তাঁর ব্যক্তিত্বের চাপে কোনো হীনমন্নতায় না ভোগেন। স্বপ্ন নিয়ের একটা দৃশ্যে বিতান এবং সুরঞ্জনার মধ্যে (নাটক স্বামী-স্ত্রী) একটা উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের দৃশ্য ছিল, সেখানে মায়াদি ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে নীরবে ওদের পর্যবেক্ষণ করতেন ও পরে অমোঘ সত্যের মত কিছু কথা ছুঁড়ে দিতেন, পুত্র ও পুত্রবধূর উদ্দেশে। এই জায়গাটায় মায়াদির ওই নীরব উপস্থিতি তেমন বাগ্ময় হয়ে উঠছিল না। আমি অ্যাকটরস্ লেফটের একেবারে ডাউনে যেখানে একটা জোনে মহামায়ার ঘরের একটা আভাষ ছিল, তার বাইরে একজনকে দাঁড় করিয়ে রাখতাম, হাতে একটা শাড়ি নিয়ে– বিতান ও সুরঞ্জনা কথা শুরু করলে মায়াদি ওদের দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে অ্যাকটরস্ লেফটের ওই জায়গা দিয়ে মঞ্চের বাইরে বেরিয়ে শাড়িটা নিয়ে আবার মঞ্চে ঢুকতেন, ওদের সংলাপের শেষে শাড়ি ভাঁজ করতে করতে নিজের সংলাপ বলতেন। আবার যে দৃশ্যে প্রমোটরের লোককে বাড়ি বিক্রীর অসম্মতি জানিয়ে খুব চাপাস্বরে বলতেন, “একবার ছিন্নমূল হয়েছি স্বেচ্ছায় আর তা হতে চাই না” তখন তার বলার দৃঢ়তার মধ্যে প্রমোটারের লোকের হাতের চায়ের কাপ নড়ে যেত বা স্বামীর বন্ধু যখন খবর আনেন নিরুদ্দিষ্ট স্বামী মারা গেছেন, তখন চিঠিটা হাতে নিয়ে, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে উদগত অশ্রু রোধ করে বলতেন, “চা খাবেন” সেই সব দৃশ্যের অভিব্যক্তি স্মরণে এলে আজও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মায়া ঘোষ আদ্যপান্ত থিয়েটারকর্মী। ‘স্বপ্ন নিয়ে’রও প্রচুর শো হয়েছে, কুচবিহারে যাওয়ার সময় রেলওয়ের কামরায়, বহরমপুর, পুরসুরা, হরিপাল, বর্দ্ধমান, চন্দননগর, হুগলী, নৈহাটি, শান্তিপুর প্রভৃতি জায়গায় কল শো সময়ে আমাদের সঙ্গে একই বাসে বা গাড়িতে অভিনয় করতে গেছেন, কোনো ভ্যানিটি প্রদর্শন না করেই। গ্রুপ থিয়েটারের সহমর্মী সহকর্মী ছিলেন মায়া ঘোষ। স্বপ্ন নিয়ের মঞ্চ-আলো জয় সেন, রূপসজ্জা শক্তি সেন, সংগীত মুরারি রায়চৌধুরী– এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই আলাপ আলোচনায় মায়াদি খুবই আগ্রহ দেখিয়েছেন। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকে মায়াদিকে অভিনয়ের বিশিষ্টতা উল্লেখ করেছিলেন, সমালোচকের দৃষ্টিতে জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষ এই নাটকটির খুব প্রশংসা করেছিলেন। রুশতি সেন মায়াদিকে নিয়ে যে বই লিখেছেন, সেখানে এই অভিনয়ের সবিশেষ উল্লেখ আছে। একটা নাটককে সার্থক প্রযোজনায় রূপান্তরিত করার পথে ‘মায়াদি’র সহচর্য-পরামর্শ স্বপ্ন নিয়ের সার্থকতার মূল কারণ। প্রণাম জানাই মায়াদি’কে, মায়া ঘোষকে।
কলকাতার গালগপ্পো'র ষষ্ঠ পর্ব লিখলেন - কিশলয় জানা

কিশলয় জানা
আজ থেকে একশো বছর আগেও কলকাতা এবং তার আশেপাশে একটি পাখিকে দেখা যেত যত্রতত্র। বক জাতীয় পাখি। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বেশ বড়সড়। কেউ কেউ বলেছেন, ডানার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি। ঠোঁটের ডগা থেকে পায়ের নখ ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি। ঠোঁটের গোড়ার বেড় ১৬ ইঞ্চি। পায়ে পালক নেই। উরুর অর্ধেকও পালকহীন, সেই অংশের পরিমাপ ৩ ফুট। যেখানেই মৃতদেহ, সেখানেই পাখিটির নিঃশব্দ উপস্থিতি। বিদেশীরা বলতেন, আরগিল (Argill), দেশীয় নামটি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে না পারায় এই বিপত্তি— পাখিটির দেশীয় নাম হাড়গিলা। বিজ্ঞানসম্মত নাম লেপটপটিলিস ডুবিয়াস। মাংশাসী বক বা স্টর্ক জাতীয় পাখি। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস ছিল, এই পাখি অবধ্য। কারণ, এর ভিতর থাকে ব্রাহ্মণের আত্মা। আর লোকে মারার চেষ্টাও করত না। তারা মনে করত, এ পাখিকে মারলে ঈশ্বরের শাস্তি নেমে আসতে বাধ্য। অতএব সে চেষ্টাও তারা করত না। কিন্তু সাহেবদের সে-কথা বোঝায় কে ? আইভেস নামে এক সাহেব তো একেবারে নাছোড়বান্দার মত লেগে ছিলেন এবং বার বার ব্যর্থ হয়ে একদিন কলকাতা থেকে সামান্য দূরে শহরতলিতে সফল হলেন তিনি, গুলি করে দৈত্যাকার পাখিটিকে মারার ইচ্ছে পূরণ হল তাঁর। এরপর থেকে কত সাহেব কত উল্লাসে এই পাখিদের নির্বিচারে মেরে ফেলেছেন, মৃতদেহ না ফেলে রেখে পুড়িয়ে দেওয়ায় তারা ক্রমশ কোণঠাসা হতে হতে সরে গিয়েছে শহরতলীর দিকে, তারপর সেখান থেকেও বিতাড়িত, মানুষের আক্রমণে হতচকিত হয়ে আস্তে আস্তে তারা হারিয়েই গেল। এখন বিশেষভাবে লুপ্তপ্রায় পাখির মধ্যে পরিগণিত। অনেককাল আগে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে একটি হাড়গিলাকে দেখেছিলাম, জানি না মিশনের পরিচর্যায় সে কত কাল বেঁচে ছিল।
এই পর্যন্ত পড়েই যে-সব পাঠক এবং স্বয়ং সম্পাদকের মুখ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে, তাঁদেরকে বলি, এই অধম নিতান্ত প্রয়োজনেই সেকেলে কলকাতার কথা বলতে গিয়ে এই পাখির স্মরণাপন্ন হয়েছে। কারণ, কলকাতায় যখন মিউনিসিপ্যালিটির মুদ্দোফরাশ ছিল না, তখন এই পাখিই যেন মুদ্দোফরাশের কাজ করত। কাককে ঝাড়ুদার পাখি বলা হলে, হাড়গিলা ছিল সেই ঝাড়ুদারদের সর্দার। এইকারণেই কলকাতায় মিউনিসিপ্যালিটির সেই গোড়ার যুগ থেকে এই পাখিকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়েছে এবং যখন ক্যালকাটা কর্পোরেশন তৈরি হল, তখন তার লোগো বা প্রতীক ছিল—দু’টি হাড়গিলা।
এমনিতে কলকাতার একেবারে গোড়া থেকেই যে মিউনিসিপ্যালিটি অর্থাৎ কর্পোরেশনের আগের রূপটি ছিল, এমনটি নয়। ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানির আওতাভুক্ত অঞ্চলে যে-কেউ জঙ্গল পরিষ্কার করে ঘরবাড়ি তৈরি করতে পারতো। এর জন্য কোম্পানির সাধারণ অনুমতি নিলেই হতো। এখনকার মতো অনুমতির জন্য তোলা দিতে হত না তখন। তবে অচিরেই লোকসংখ্যা বাড়তে থাকায় রেজিষ্ট্রেশনের নিয়ম চালু হয়। চুক্তিপত্র বা রেজিষ্ট্রেশন করানোর জন্য প্রথম দিকে সাহেবদের শতকরা দু’ টাকা এবং দেশীয়দের ক্ষেত্রে শতকরা পঁচিশ টাকা দিতে হত। তবে ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যাল আইনে ব্যাপক রদবদল হয়। এই সময় থেকেই দেশি-বিদেশি পার্থক্য তুলে দিয়ে সকলের ক্ষেত্রেই শতকরা পাঁচ টাকা হারে রেজিষ্ট্রেশন ফি’ চালু হয়। সকলকেই রেজিষ্ট্রেশন করতে হত, অন্যথায় মোটা হারে জরিমানা দিতে হত। প্রথম থেকেই অনেকেই ইংরেজদের এলাকায় বসবাসের জন্য এসে ভিড় করেছিলেন, আসল চাহিদা ছিল একটু ভদ্রস্থ জীবনের। পলাশির যুদ্ধের আগে থেকেই কিন্তু কলকাতায় ক্রমশ লোকবসতি বাড়ছিল। ঘরবাড়ি তৈরির পর বসবাসের জন্য কিছু কিছু নিয়ম ছিল, যা মানতে বাধ্য ছিল বাসিন্দারা, অন্যথায় জরিমানা দিতে হত। ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে কাউন্সিলের আদেশে দেশীয় অধিবাসীদের জরিমানার টাকায় শহরের মধ্যে এবং আশেপাশের খানাখন্দ ও ডোবা ভরাট করা এবং নর্দ্দমা পরিষ্কার করা হবে স্থির হয়। কেউ কেউ এই ব্যবস্থাকেই কলকাতার প্রথম মিউনিসিপ্যাল্ ব্যবস্থা বলে মনে করেন।
কলকাতা, সূতানুটির তুলনায় গোবিন্দপুরের গ্রাম্য ভাবটা বেশি ছিল। এই কারণে ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে গোবিন্দপুরের খাজনা বাকি অংশের চেয়ে কিছুটা কমানো হয়েছিল। এই সময় থেকেই শহরটিকে একটু পরিকল্পিত আকারে গড়ে তোলার জন্য ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। এই কারণে যত্রতত্র অপরিকল্পিতভাবে ঘরবাড়ি তৈরিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। বিশেষ করে ফোর্ট উইলিয়মের আশেপাশে দেশীয়দের ঘরবাড়ি তৈরি নিষদ্ধ করা হয় এবং অন্যত্রও যেখানে-সেখানে ঘরবাড়ি তৈরি কিংবা পুকুর খনন ইত্যাদির ব্যাপারে নিষেধ করে ফোর্ট উইলিয়মের দরজায় নোটিশ লটকে দেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। ১৭১০ খ্রিষ্টাব্দেই ফোর্টের মধ্যে ও আশেপাশের এলাকার উন্নতির জন্য জঙ্গল পরিষ্কার এবং জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত করার জন্য বক্সী-কে আদেশ দেওয়া হয়। বক্সীরা আসলে একালের পিডব্লিউডির মতো কাজ করতেন। বক্সীদের মাথায় একজন সাহেব থাকতেন, কিন্তু বাকি কাজ দেশীয়দের দিয়েই করানো হত।
তবে কলকাতার জমিদারি লাভ করার পরেও দীর্ঘদিন কলকাতার উন্নয়ন নিয়ে কোম্পানির কোন মাথা ব্যথা ছিল না। তাঁরা মূলত ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। এর জন্য জমিদারি এলাকায় পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা দেখা দিচ্ছিল। এই সব কারণেই ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে কাউন্সিলের মধ্যে ‘কালেক্টর’ পদ সৃষ্টি হয় এবং র্যাল্ফ শেলডন প্রথম কালেক্টর হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁর বেতন ছিল বছরে দু’ হাজার টাকা। তাঁর কাজ ছিল মূলত ব্যবসায়িক ও বাস্তু জমির জন্য পাট্টা দেওয়া, কর ও জরিমানা আদায় এবং আবাদী জমির বিলি-বন্দোবস্ত করা। কলকাতার বাসিন্দা, ব্যবসায়ী প্রভৃতির কাছ থেকে আদায় করা এই করের পরিমাণ নেহাত কম ছিল না, উত্তরোত্তর বাড়ছিল বলা যায়। ফলে নেহাত কম রাজস্ব এবং জরিমানা বাবদ আয় ছিল না কোম্পানির। তাছাড়া যে-সব প্রজা সময়মতো কর দিতে পারতেন না, তাঁদের ধরে আনা হত এবং চাবুক ইত্যাদি দিয়ে নির্মম ভাবে শাস্তি দেওয়া হত। অনেককাল ধরে এই ধারা বজায় রেখেছিলেন ‘ব্ল্যাক জমিদার’ পদে আসীন নন্দরাম সেন এবং গোবিন্দরাম মিত্র। ‘ব্ল্যাক জমিদারে’রা মূলত ছিলেন কালেক্টরকে সাহায্য করার জন্য নিযুক্ত প্রধান দেশীয় কর্মচারী। দেশীয় হওয়ার কারণে সাহেবের তুলনায় তাঁদের বেতন ছিল যৎসামান্য, তবে তা তাঁরা উসুল করে নিতেন বাঁকা পথে। এবং সেই পথ প্রয়োজনে নির্মমতার চরমে পৌঁছাতে দেরি করত না। এই গোবিন্দরাম মিত্র কিন্তু পরবর্তীকালের খ্যাতনামা কিংবা কুখ্যাতনামা বাবুদের আদিপুরুষ। তাঁর জীবনযাপনের কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপই অনুসরণ করেছেন উত্তরকালের বাবুরা। সে-সব কথা বারান্তরে বলা যাবে।
করের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কর আসত বাজার কর থেকে। এর পরেই ছিল গৃহ কর, চৌকিদারি কর, তৌলদারি কর, নগরশুল্ক, আবগারি কর, নৌকা-ফেরিঘাট-রাস্তা ও সেতু থেকে আদায়ীকৃত কর, স্ট্যাম্প ডিউটি, কলকাতার সোন্দর্যায়নের কর, আমদানী কর অর্থাৎ বহিঃশুল্ক এবং অন্যান্য ছোটোখাটো কর। সেকালে কলকাতার রাস্তাঘাট মোটেই নিরাপদ ছিল না। খাস কলকাতার পথেঘাটে উনিশ শতকের শেষদিকেও চুরি-ছিনতাইয়ের প্রাদুর্ভাব ছিল। কলকাতা থেকে একটু শহরতলীর দিকে গেলেই আর কথা ছিল না। চুরি-ছিনতাই-ডাকাতি এ-সব ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। সেকালের পত্রপত্রিকা খুললেই তার অনেক বিবরণ পাওয়া যাবে। এমনকি বিশ শতকের গোড়ার দিকেও বালিগঞ্জ, গোলপার্ক ইত্যাদি অঞ্চলে এলে সন্ধ্যার দিকে আর ফেরার গাড়িঘোড়া পাওয়া যেত না। বড় রাস্তা পর্যন্ত হেঁটে এসে ট্রাম ইত্যাদির আশায় হাপিত্তেস করে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। গোলপার্কে রবীন্দ্র-সরোবরের উল্টো দিকে ছিল কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বাড়ি। চারপাশে ধানী জমি, ঝোপঝাড়-গাছপালা। বন্ধুবর যতীন্দ্রমোহনের বাড়িতে প্রায়শই মজলিশ বসত কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের। কিন্তু ফেরার সময় একটু দেরি হয়ে গেলেই বিড়ম্বনায় পড়তে হত। এ-কথা জানিয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। হেমেন্দ্রকুমার রায়ও আসতেন সেই আসরে। গল্পে-গল্পে রাত হয়ে গেলে অসুবিধার শেষ থাকত না। সেই রকম একদিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি লিখে ফেলেন তাঁর বিখ্যাত ‘কঙ্কাল-সারথি’ গল্পটি। মনে রাখতে হবে, এ-হল বিশ শতকের কলকাতার কথা। কিন্তু তারও একশো বছরেরও আগে কলকাতা যে ছিল খানা-খন্ড, ঝোপঝাড়, জঙ্গল-পুকুর, মশা-মাছি এবং চোর-ডাকাত অধ্যুষিত একটি অস্বাস্থ্যকর অঞ্চল, তাতে সন্দেহ নেই। মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থা চালু হওয়ার গোড়ার যুগ থেকেই সাহেব শাসকেরা ক্রমেই সচেতন হচ্ছিলেন, বিশেষ করে আইন-প্রশাসনের কাজকর্মের এলাকা সম্প্রসারণের ব্যাপারে। চৌকিদারি কর ছিল সেইরকম একটি কর, যেখানে রাস্তাঘাটে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হত এই খাতে আদায় হওয়া টাকা থেকে।
তৌলদারি কর ছিল এইরকম একটি কর, যেখানে জাল-জুয়াচুরি প্রতিরোধ করার জন্য কোম্পানি বছরে দু’বার ব্যবসাদারদের দাঁড়িপাল্লা-বাটখারা পরীক্ষা করতেন। ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বছরে চারবার পরীক্ষা করার নিয়ম চালু হয়। তবে তা সত্ত্বেও খাদ্যে ভেজাল এবং বাটখারায় জাল-জুয়াচুরি আটকানো যায় নি। হত্যা-প্রতিহত্যাও ছিল খাস কলকাতার স্বাভাবিক চিত্র। তবে বিচার দীর্ঘায়িত হত না। হত্যা করলে সচরাচর ফাঁসির সাজা দেওয়া হত। ডব্লিউ.এইচ. কেরি এই রকম কয়েকটি ঘটনার কথা শুনিয়েছেন। ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জুন ম্যানিলার এক অধিবাসীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেয়। লোকটি দেশীয় এক মহিলাকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন করে। শনিবার ১৩ জুন সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তার ফাঁসির সাজা হয়। আর ফাঁসির স্থানটিও নির্বাচন করা হয় অভিনব জায়গায়। লালবাজার যাওয়ার রাস্তায় যে চৌমাথা পড়ে, সেখানেই অপরাধীকে সর্বজনসমক্ষে ফাঁসি দেওয়া হয়। তবে ইংরেজ অধিবাসীরা অপরাধ করলে তার বিচার সব ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার সঙ্গে করা হত না বলে অভিযোগ। ১৮১৩ সালেও পাঁচ জন পোর্তুগিজকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয় ‘এশিয়া’ জাহাজের ক্যাপ্টেন স্ট্যুয়ার্টকে হত্যার অপরাধে। সেক্ষেত্রেও পুরানো কুঠিঘাটে সবার সামনে তাদের ফাঁসি কাঠে ঝোলানো হয়। ১৮২৮-এও উন্মুক্ত জায়গায় এক ফকিরকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। ফকিরটি হাওড়া ঘাটে উইলিয়ম ব্যুচাম্প নামে একটি শিশুকে হত্যা করে, সম্ভবত তন্ত্রসাধনা করতে গিয়ে। ঘাটের অদূরেই একটি স্কুলের মাঠে ফকিরকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়। অনেক দেশীয় লোক সেদিন সেই ফাঁসি দেখবার জন্য ভিড় জমিয়েছিল। মূলত অপরাধীদের সতর্ক করতেই উন্মুক্ত স্থানে ফাঁসি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। তা সত্ত্বেও পারিবারিক হিংসা কিংবা পারস্পরিক লড়াই-ঝামেলা-হত্যা ইত্যাদি বন্ধ হয় নি।
উনিশ শতকের আগেই ১৭৩০-৩২ নাগাদ কলকাতা কর্পোরেশনের জন্ম হয়। এর কার্যকরী সর্বোচ্চ কর্তা ছিলেন মেয়র। তাঁকে সাহায্য করতেন নয় জনের একটি দল। তাঁদের বলা হত অল্ডারম্যান। হলওয়েল সেসময় কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এই সময় মিউনিসিপ্যালিটি বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু কাজ করলেও বাস্তবে উনিশ শতকের আগে কলকাতাকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার কাজ এগিয়েছিল সামান্যই। এমনকি ওয়ারেন হেস্টংসের সময়েও কাজ বলবার মতো কিছু অগ্রসর হয় নি। ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা কাউন্সিলের বিলেতে পাঠানো চিঠি থেকে জানা যায় যে, শহরে নর্দমা কাটার কাজ শুরু হয়েছে, এর ফলে শহরে স্বাস্থ্যপূর্ণ পরিবেশ গড়ে উঠবে। লালদিঘি এর আগে জনসাধারণের স্নানের জায়গা ছিল, এমনকি ঘোড়া প্রভৃতিকে স্নানও করানো হত এখানে। কিন্তু ১৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে কোম্পানির আদেশ বলে এই নিয়ম বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে এটি বেশ কিছুকালের জন্য হয়ে ওঠে শহর কলকাতার অন্যতম জলের ভাঁড়ার, মূলত সাহেবপাড়ার জল সরাবরাহের অনেকটা সামাল দিত এই দিঘি। ইংরেজদের ম্যাপে একে ‘গ্রেট ট্যাঙ্ক’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একে মাঝখানে রেখে গড়ে উঠেছিল সেকালের সাহেবপাড়া, আজ অবশ্য বিবাদিবাগের একদিকে সে নেহাতই সাধারণ পুকুর হয়ে পড়ে আছে। যদিও সাম্প্রতিককালে সেখানে আবার জনসাধারণের স্নান ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে উইলিয়ম ওয়েল্সের ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে আঁকা ম্যাপে গ্রেট ট্যাঙ্কের অনতিদূরে আর একখানি ছোট পুকুর দেখানো হয়েছে, যা পরবর্তীকালের ম্যাপগুলিতে দেখা যায় না। সম্ভবত এটি একটি ছোট পুকুর ছিল, যা পরবর্তীকালে নগরায়নের নামে বুজিয়ে ফেলা হয়। যদিও এত কিছু ভাবা হলেও, ১৮২০-র আগে পাকা রাস্তা ছিল না কলকাতায়। এই সময় থেকেই পঁচিশ হাজার টাকা পাকা সড়ক তৈরির খাতে নির্দিষ্ট করা হয়। লর্ড ওয়েলেসলির আমলে সার্কুলার রোড পাকা সড়কে পরিণত হয়। খাস কলকাতায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত জঙ্গল বাগান ইত্যাদি প্রভূত পরিমাণে ছিল। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহামারির পর কোম্পানি একটি বিজ্ঞাপন মারফৎ জানিয়ে দেয় যে, কোম্পানির সীমার মধ্যে কমলালেবু ও অন্যান্য ফলবান বৃক্ষ ছাড়া অন্যান্য গাছ যে কেউ নিজের খরচে কেটে নিয়ে যেতে পারে। কোম্পানির আসল উদ্দেশ্য ছিল, শহরের সীমার মধ্যে জঙ্গল পরিষ্কার করা। এই বিজ্ঞাপনের ফলে কোম্পানির নিজের এক পয়সা খরচ হল না, অথচ জঙ্গল ইত্যাদি সাফ হয়ে গিয়ে নতুন নগরায়নের জমি তৈরি হয়ে গেল, এটাই হল আসল ব্যাপার। সেই সময় থেকেই জঙ্গল সাফ করে, সবুজ ধ্বংস করে ইঁট-কাঠ-পাথরে স্তুপিকৃত কলকাতার প্রকৃত পথ চলা শুরু হল। কলকাতা ও তার উপকন্ঠের সীমানা নির্দ্ধারিত হয় ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দে। এই সময় থেকেই জাস্টিস্ অব্ পিস্ নামের কমিটির হাতে মিউনিসিপ্যালিটির ভার ন্যস্ত হয়। উনিশ শতকের সূচনা থেকেই লটারি কমিটি ইত্যাদির হাত ধরে ক্রমশ কলকাতা আজকের কলকাতা হয়ে উঠতে শুরু করে।
'পাল্প ফিক্শন'এর আনাচে কানাচে ঢুঁ মারলেন - সৈকত নন্দী
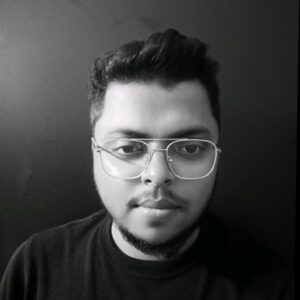
সৈকত নন্দী
পাল্প ফিকশন এবং ইত্যাদি..
বাংলা সিনেমা বা ওয়ার্ল্ড সিনেমা নিয়ে যারা একটু হলেও চর্চা করেন, তারা জানেন যে কান পাতলেই একটি নতুন শব্দ শোনা যাচ্ছে। ‘পাল্প ফিকশন’; হটাৎ-ই ধূমকেতুর মতন আবির্ভাব যেন। কি মনে হচ্ছে, এক্কেবারে নতুন জনরা? আজ্ঞে! না। আঠারো শতকে যখন টেলিভিশনের আনাগোনা হয়নি তখন বিনোদনের মাধ্যম ছিল এই পাল্প ফিকশন। আদতে বিনোদন মাধ্যমটাই এরকম। একরকম দেখতে দেখতে সেই ‘এক্সাইটমেন্ট’টা আর আসতে চায় না। যারা বিনোদন বণ্টনের দায়ভাগ নিয়েছেন তারাও অবসরে এই কল্পনাই করেন, ‘আরও কি নতুনত্ব আনা যেতে পারে?’ কিন্তু কোথাও গিয়ে সেই চিন্তার পরিসর সংকীর্ণ হয়ে যায়। তখন স্মৃতির মণিকোঠায় টোকা পরে পুরোনো জিনিসের নতুনীকরণ। ঠিক এরকমই এখন ‘পাল্প ফিকশন’ এর ডাক পড়েছে। আর কেল্লাফতে! মানুষ এতেই মজেছে। কিন্তু কি এই ‘পাল্প ফিকশন’?
মূলত আঠারো শতকে কম সময়ের বিনোদন বলতে ‘পাল্প ফিকশন’ কেই বোঝানো হতো। কখনো কমিকসের আকারে, বা লেখার আকারেও এর প্রকারভেদ দেখা যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যস্ততা বেড়েছে, কিন্তু তা বলে বিনোদন বন্ধ থাকবে? মোটেও না, তাই বেশি গবেষণা বা সাহিত্যের নানান চরিত্রের গভীর রূপরেখা না এঁকে একদম সোজা সাপ্টা ও সরাসরি বিনোদনকেই বলা যেতে পারে ‘পল্প ফিকশন’। বর্তমান সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বোঝাতে গেলে, বলতে হয় যাদের কাছে পর্যাপ্ত সময় বা টাকা বা দুটোর কোনোটাই নাই, তাদের কাছে কম সময়ের বিনোদন হল ইনস্টাগ্রাম রিলস। ২ঘন্টার সিনেমা দেখার সময় যার নেই, সে অফিস থেকে ফেরার পথে পার্শ্ববর্তী নানান অবাঞ্ছিত সিচুয়েশনকে ভুলতে ডুব দেয় ফেসবুকের ফিডে আসতে থাকা কোনো সিনেমার ২-৩ মিনিটের ক্লিপিংসে। হ্যাঁ! এইটাই ‘পাল্প ফিকশন’-এর আধুনিক সংজ্ঞা। কিন্তু খেলা এখানেই শেষ নয়। বিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে যে ডোপামিন আমাদের মস্তিষ্কে নিঃসরণ হয়, সেটা একই জিনিস বা সাধারণ জিনিস দেখতে দেখতে আর নিঃসরণ হয় না। তখন মানুষ কল্পনার মধ্যে ডুব দেয়, নিজের ডার্ক ডিসাইরের রোলার কোস্টারে চরে। তখন যৌনতা, ক্রাইম যেন আলাদা সুখানুভুতি দেয় মানুষকে। ষড়রিপুর অধীন আমি আপনি কিন্তু হাজার নিষেধ থাকলেও তখন কিন্তু এই নিষিদ্ধ হাতছানি উপেক্ষা করতে পারিনা। আর এটাই ‘পাল্প ফিকশন’-এর মূলধন । তার ওপরে ভিত্তি করেই কিন্তু হরর, ক্রাইম, থ্রিলার, সাইন্স ফিকশন বা পর্ন গোছের জনরার জন্ম। সেখানে গল্পের গরু আকাশ গঙ্গা হয়ে আরও অন্যান্য ইউনিভার্স ঘুরে আসে অনায়াসেই। পাঠক তখন যুক্তির ঘরে তালা দিয়ে, ডোপামিনের আরাধনা করে। অবশ্য ‘পাল্প ফিকশন’-এর তরতরিয়ে বেড়ে ওঠার পিছনে অবসাদও দায়ী। বিশ শতকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন মানুষ ঘরবাড়ি তথা দেশছাড়া, কাজের সঙ্গে সঙ্গে অর্থে টান পড়েছে, তখন বাস্তবকে ভুলে এক কল্পনার মহাসমুদ্রে ডুব দেয় ‘পাল্প ফিকশন’-এর মতন মণিরত্নের খোঁজে। আশা করা যায় এই স্বল্প পরিসরের ব্যাখ্যাতে দর্শক সহজেই পেতে পারবেন ভিন্নধর্মী বিনোদনে ‘পাল্প ফিকশন’ এ সুলুক সন্ধান।
প্রেমের অমর চিরাগ, আলাপ আলোচনায় - সায়ন ভট্টাচার্য

সায়ন ভট্টাচার্য
আমাদের চারপাশে আদর স্বপ্নের ছায়া। কিন্তু স্বপ্ন, সে তো স্বপ্নই। বাস্তবে ধুলোবালিছাই জীবনের অনন্ত অবারিত ফাঁস। কত হাজার নির্মম চোখ কষাঘাত করে চলেছে দিনের পর দিন।
উষ্ণ তীব্র রোদের ছুরি যখন মাথা বুক ছিঁড়ে আমাদের ফালাফালা করে দিচ্ছে, যখন নিদারুণ হতাশার অতল অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে একটা দেশের সঙ্গে একটা তরুণ প্রজন্ম- তখন আশাবাদকে নিয়ে আসবে এই জ্বালাপোড়া সমাজের বুকে? এমন থিয়েটারের খোঁজ সত্যিই কি আছে— যার মধ্যে দিয়ে মানুষ একটা বাঁচার স্বপ্ন দেখতে পারে? নিজের ছেলেবেলার নস্টালজিয়ায় ফিরে যাওয়াকে যদি পলায়ন বলা কারোর মনে হয় তবে সেই পলায়ন ভালো— বাঁচার রসদের জন্য ভালো।
আলাদিন-এর কাহিনির বর্ণনা নিয়ে এখানে কোনও কথা বলছি না। আরব্য রজনী-র উপকথার রাজ্যে প্রতিটি মানুষ পাড়ি দেয় জীবনের কোনো না কোনও বাঁচার মুহূর্তে। আসলে মানুষ বড্ড ভোগী, যে বিত্ত চায় অগাধ, সে চায় বদর-উল-বদর-এর মতো রূপসী রাজকন্যা যার সঙ্গে মায়া পরীর সাহায্যে অনেক দূর ভেসে আসা যায়। আলাদীন-এর চৌর্যবৃত্তি থেকে নিষ্কৃতির জন্য খুঁজে ফিরতে থাকে যে আশ্চর্য প্রদীপ, মানব সভ্যতা তো খুঁজে ফিরছে সেই আশ্চর্য সমপর্দ। কিন্তু সানি চট্টোপাধ্যায় নাটকটিকে একদম নতুন একটি কাঠামোয় নিয়ে গেছেন। আশ্চর্য প্রদীপের মধ্যে লুকিয়ে থাকা জিন-এর যে দাসত্ব, সেই দাসত্বের বিরুদ্ধে নাটকীয় সংকটকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। এইখানেই নাটকটি একটি অন্য মোড় নেওয়ার চেষ্টা করেছে, এবং অবশ্যই সফল হয়েছে।
আলাদিন খুব সহজ সরল ভাবেই একদিন রাজকন্যা বদর-উল-বদুর-কে কিছু প্রহরীর হাত থেকে রক্ষা করে, যদিও সে অজ্ঞাত ছিল রাজকন্যার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে। তারপর হাতে যে আশ্চর্য প্রদীপ আসে সে প্রদীপ আসলে সামাজিক সংকট-জাফর-এর মত কুখ্যাত শাসকরা চায়— ‘চিরাগ’ এর সম্পূর্ণ দখল, ক্ষমতাই তো মায়া! কার হাতে থাকবে জিন— প্রশ্ন একটাই, কিন্তু জিন তো জানে কে, কীভাবে তাকে ব্যবহার করবে– দাসত্বের কাছে বন্দি জিন স্বাধীন হতে চেয়েছে আলাদিন ও বদর-উল-বদর-এর প্রেমের সত্যের মতো। ‘আলাদিন’ নাটক যেন মনে করিয়ে দিল প্রেমই হলো সেই চিরাগ, যার সাহায্যে যে কোনও সমস্যা সংকুল পথ অতিক্রম করা যায়।
এইভাবেই একদিন জাফর বন্দি হবে প্রদীপের অন্ধকারে। মিনার্ভা রেপার্টরি কর্মশালা ভিত্তিক এই প্রযোজনায় সানি একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন— একটি মিথকে কীভাবে রাজনৈতিক কলুষিত সময়ে পুনর্নির্মাণ করে সত্যের জয়কে সুনিশ্চিত করলেন।
এবার আসি নাট্যের প্রায়োগিক দিকে। সানি চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনা, অদ্রীশ কুমার রায়-এর মঞ্চের নির্মাণ ও সমর পাড়ুই-এর আলো মিলে যেন একটি ব্রডওয়ে থিয়েটারের মঞ্চমায়া তৈরি করেছিল। পোশাক পরিকল্পনায় সংহিতা দত্ত চক্রবর্তী, জ্যোতির্ময় পণ্ডিত ও ঊষার আচার্য – বেশ গবেষণা করে কাজটা করেছেন।
মিনার্ভা রেপার্টরির অভিনেতারা ভবিষ্যৎ বাংলা থিয়েটারের সম্পদ। প্রত্যেকে নিজের চরিত্রে অনবদ্য। শারীরিক অভিব্যাক্তি, নৃত্যের ধরণ, কিংবা গানের সঙ্গে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ফিউশন— গোটা টিমওয়ার্ক অনবদ্য। তার মধ্যেও বিশেষ ভাবে বলতে হয় ‘জাফর’ চরিত্রে অরিন্দম সরদার, অবশ্যই ‘আলাদিন’ চরিত্রে শুভ্রদীপ বণিক। শুভ্রদীপের মঞ্চের মধ্যে অভিনয় ও এনার্জি অতুলনীয়। ‘বদর-উল-বদুর’ চরিত্রে নিশা হালদার-এর অভিনয় এই নাটকের সম্পদ। নিজেকে দৃপ্ত ভাবে আত্মপ্রকাশ করার যে অদ্ভূত মাধুর্য নিশা তৈরি করেছেন তাতে নাটকের উজ্জ্বলতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। চারজন জিনি-র চরিত্রে সঞ্জয় চক্রবর্তী, সুজন ঘোষ, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, সানি চট্টোপাধ্যায়— গানে, নাচে, অভিনয়ে সমান গুরুত্ব সহকারে কাজ করেছেন।
তরুণ নাট্যকর্মীরা কত গভীর মনোযোগ সহ নতুনভাবে থিয়েটারের যে পরীক্ষা নিরীক্ষা তারা চালাচ্ছেন, আমাদের উচিত অবশ্যই সেই কাজটিকে গভীরভাবে দেখা। ডিজনি-র দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া সহজ, কিন্তু এতটা গভীরভাবে তাকে মঞ্চে তুলে আনার জন্য সানি চট্টোপাধ্যায়ের অবশ্যই কুর্নীশ প্রাপ্য। বাংলা থিয়েটারের আবহাওয়ায় সিনোগ্রাফি নিয়ে যে বিবিধ তর্ক বিতর্ক হয়, রেপার্টরির অভিনেতারা দেখিয়ে দিল, একটা গোটা কলকাতার বুকে কীভাবে নামিয়ে আনা যায় একটা আরব্য রজনীর দেশ।
'গোরা ৩' পর্দায় আসার অপেক্ষায়- বৃতা মৈত্র

অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তীর নামটুকুই যথেষ্ট– সে মাধ্যম যা-ই হোক। দুর্বলতম চিত্রনাট্যও উৎরে যায় ঋত্বিকের শক্তিশালী অভিনয়ের গুণে। এহেন ঋত্বিকের সাবলীল অভিনয়ে একটু ভিন্ন (বিচিত্রও বলা যায়) অবতারের বাঙালি গোয়েন্দা ‘গোরা’ যে দর্শকের বেশ পছন্দের হয়ে উঠবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। বলতে দ্বিধা নেই, হইচই-এর ওয়েব সিরিজ ‘গোরা’ প্রথম সিজন থেকেই দর্শক দরবারে একটা আলাদা ক্রেজ তৈরি করতে পেরেছে এই কারণেই। গৌরব সেন ওরফে গোরা হিসেবে নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন ঋত্বিক।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ ‘গোরা’ একজন খ্যাপাটে গোছের মানুষ। সে হল সিরিয়াল কিলার স্পেশালিস্ট। এদিকে সে কোনও হিন্ট মনে রাখতে পারে না, লোকজনের নামও ভুলে যায়। কমেডি এবং থ্রিলের মিশেলে তৈরি এই সিরিজ। গোরার অঙ্গভঙ্গি, বেসুরো গান গাওয়া, নাম মনে রাখতে না পারায় যে মজাটা সৃষ্টি হয়, সেটাই দর্শককে মাতিয়েছে। নিজের অভিনয়শৈলীর মাস্টার স্ট্রোক খেলেছেন ঋত্বিক এখানেই। তাঁর অঙ্গভঙ্গি খানিকটা উচ্চকিত হলেও তা দেখে বিরক্তি নয়, হাসি পায় দর্শকের। তার প্রতিভায় অবশ্য ঘাটতি নেই। একজন মানুষকে একবার দেখে, গোরা তার সম্পর্কে অনেককিছু বলে দেওয়ার পাশাপাশি সাধারণ কথার মধ্যে থেকেই খুঁজে বের করে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রসঙ্গত, গোরা চরিত্রটির সঙ্গে অনেকেই কোথাও গিয়ে বিবিসি-র শার্লক হোমসের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন। কারণ, সেও একজন সোশিওপ্যাথ।

পরিচালক সায়ন্তন ঘোষাল ‘গোরা’র প্রথম সিজনের গল্প পরিবেশনায় যে স্মার্টনেস দেখান, তাতে আট পর্বের সিজনটি রীতিমতো বেঁধে রেখেছিল দর্শকদের। ঋত্বিকের পাশাপাশি তার সহকারী ও গোরার বোন কঙ্কার (অনন্যা সেন) হবু বরের চরিত্রে সুহোত্র মুখোপাধ্যায়ও দারুণ সঙ্গত করেছেন। ঋত্বিক-সুহোত্রর অনস্ক্রিন যুগলবন্দী ম্যাজিক সৃষ্টি করে পর্দায়। প্রথম সিজনে তিনজন লেখকের খুনের কিনারা করতে গিয়ে হিমশিম খাওয়া পুলিশ স্মরণাপন্ন হয় গোরার। অদ্ভুত খুনের ধরন–তিন লেখকের দাঁত উপড়ে, সেখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে পেনের নিব। এছাড়াও আরও একটি সমস্যা নিয়ে আসে সোমলতা (ইশা সাহা)। মূল কাহিনিটি আবেগমাখা, তার সঙ্গে থ্রিল-কমেডির বুনন, ঋত্বিকের লুক, সকলের অভিনয় এবং সর্বোপরি সিরিজের চিত্রনাট্য ‘গোরা’-কে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল।

এরপর এলো ‘গোরা ২’। এবার সিরিজের ক্রিয়েটর সাহানা দত্ত, পরিচালকের আসনে জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। এই সিজনে কোথাও যেন থ্রিলের তুলনায় কমেডি গুরুত্ব পায়। আট পর্বের সিজন ২-এর কাহিনির সূত্রপাত, ন্যাড়া মাথার কারণে বিয়ে হচ্ছে না গোরার। কিন্তু সে পণ করেছে দু’সপ্তাহের মধ্যে পাত্রী খুঁজে বিয়ে করবে। এমতাবস্থায় তার কাছে একটি কেস নিয়ে হাজির হয় শ্রেয়সী মিত্র (উষসী রায়)। শ্রেয়সীর দিদির তিনবছরের বাচ্চা মেয়ে রক্তবমি হয়ে মারা গিয়েছে। সেই বাড়িতে আরও দুটি বাচ্চা মেয়েও একই রকম উপসর্গ নিয়ে মারা গিয়েছে। শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সন্দেহ শ্রেয়সীর দিদিকেই। কেন? এরই পাশাপাশি একটি নার্সিংহোমে দু’জন নার্স ও একজন ওয়ার্ড বয় সিঁড়ি থেকে অস্বাভাবিক ভাবে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছেন। একাধিক ব্যক্তি সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে। প্রশ্ন হলো, ঘটনা দুটি কী একসূত্রে গাঁথা?
এদিকে তদন্ত করার সময় গোরার বাড়ির পরিস্থিতিও অদ্ভুত। তার মায়ের (অনুরাধা রায়) চোখ অপারেশন হয়েছে। তাঁকে দেখার জন্য অর্ণা (মানালি দে) নামে একজন নার্সকে রাখা হয়েছে। কিন্তু গোরা অর্ণাকে পছন্দ করে না। এমতাবস্থায় সবদিক সামাল দিয়ে গোরা রহস্য উদঘাটন করতে পারে কি? তার বিয়ে কি হয়? এর উত্তর বলে দিলে সিরিজ দেখার মজা মাটি! তাই ওয়েব পর্দায় দেখাই ভালো। আগের সিজনের মতোই এবারেও পুলিশ ইন্সপেক্টর তারাপদ সরখেলের চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিজিৎ গুহ। এছাড়াও অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন মিমি দত্ত, বিপ্লব দাশগুপ্ত প্রমুখ।
এই সিজনেও ঋত্বিক-সুহোত্রর অনস্ক্রিন কেমিস্ট্রি নজর কেড়েছে দর্শকের। ঋত্বিক-মানালি জুটিও বেশ কিছু মজাদার মুহূর্ত তৈরি করে। শেষে গিয়ে যেভাবে এই দুই চরিত্র কাছাকাছি আসে, সেটা যথেষ্ট উপভোগ্য। যে পদ্ধতিতে এখানে খুন দেখানো হয়েছে, সেটিও ইন্টারেস্টিং। তবে, কিছু দৃশ্যকে অহেতুক টেনে বড় করার পাশাপাশি জোর করে কমেডি তৈরির চেষ্টা হয়েছে, যা কিছুটা অনাকাঙ্ক্ষিত। যদিও নিজের অভিনয় দিয়ে চিত্রনাট্যের খামতি অনেকটাই ঢেকেছেন ঋত্বিক। বেশ কিছু দৃশ্যকে প্রায় একাই টেনেছেন তিনি। এবারেও তাঁকে যোগ্য সহায়তা করেছেন সুহোত্র। শেষ খবর, খুব শিগগিরই আসছে ‘গোরা ৩’। সব দোষ-ত্রুটি বাদ দিয়ে শুধু ঋত্বিকের অভিনয় দেখার জন্যই সিজন ৩-এর অপেক্ষায় বাংলা ওয়েব দর্শক।

