ভাণ পত্রিকা
একচল্লিশতম সংখ্যা || বত্রিশতম ই-সংস্করণ || সেপ্টেম্বর ২০২৩
সম্পাদক :

সম্পাদনা সহযোগী :

প্রচ্ছদ :

নক্সা পরিকল্পক :

অন্যান্য কাজে :








ভাণ-এর পক্ষে:
পার্থ হালদার
কর্তৃক
৮৬, সুবোধ গার্ডেন, বাঁশদ্রোণী, কলকাতা : ৭০০০৭০ থেকে প্রকাশিত। যোগাযোগ : ৯৬৪৭৪৭৯২৫৬
( হোয়াটসঅ্যাপ ) ৮৩৩৫০৩১৯৩৪ ( কথা / হোয়াটসঅ্যাপ )
৮৭৭৭৪২৪৯২৮ ( কথা ) bhaan.kolkata@gmail.com ( ই – মেল )
Reg. No : S/2L/28241
সম্পাদকের কথা
।। সম্পাদকের কথা।।
।।সেপ্টেম্বর ২০২৩।।
দেশটার হলো কী? কোটি কোটি লোক সমস্বরে বলতে শুরু করল ‘আলাদা’ খারাপ ‘একতা’ ভালো!! একতা ভালো জানতুম, এক হয়ে থাকা ভালো শুনতুম কিন্তু সব ‘এক রকম’ হয়ে যাবে! এ কথা ভাবতে গেলেই মিনিমাম এস্থেটিকস দেখভালের নার্ভগুলি প্রতিবাদে ধর্নায় বসতো। আর আজকাল দেখি, যারা আমরা-ওরা, সাদা-কালো, হিন্দু-মুসলিম, ধনী-গরিব, শহর-গ্রাম, বড়লোক-ছোটো জাত, নারী-পুরুষ, হিজড়ে-বেশ্যা, এদেশি-ওদেশি— ধুয়ে প্রতিদিন জল খান, তারাই কোন অশালীন চক্রান্তে ‘এক’ এর গুণগান গাইতে শুরু করলেন!
একের মধ্যে অনেক আর অনেকের মধ্যে এক— এই ছিল গৌরবের। তেত্রিশ কোটি দেবতা নিয়ে আমাদের মন্দিরে ঠোকাঠুকি ছিল না। থিওলোজির হাজারো ব্যাখ্যান চণ্ডীমণ্ডবের সান্ধ্যআসরে আনন্দের অভাব ঘটায়নি। চণ্ডীমণ্ডবের বাউল গেয়েছে। বাউলানির স্মরণ সভায় গান ধরেছে ফকির। সকালের আজান আর সন্ধ্যার আরতি বহিরঙ্গে আলাদা হলেও লক্ষ্যে অভিন্ন ছিল। ছিন্নভিন্ন ভাবধারাদের নিয়ে শুশ্রূষার সাম্যগীতি গাইবার মহাজনদের অভাব ছিল না। বাপের তিনটি ছেলে, তিন স্বভাবের হয়েও তারা যে বাপের বড়-মেজো-ছোটো তাই নিয়েও গোল বাঁধেনি। গোলাপ, জুঁই, বেল-এর সঙ্গে কুমড়ো ফুল তাদের নিজত্ব বজায় রেখেই মর্যাদা রক্ষা করেছিল বাগানের। সব ফুলকে এক করে দাও, সব রঙ একরঙা করে দাও, সব গন্ধকে একগন্ধী করে তোলো- এমন ফুলিশ কথা কখনো শুনতে হয়নি।
অভিন্ন বিয়ে, অভিন্ন বিচ্ছেদ, অভিন্ন আইন, অভিন্ন সিলেবাস, অভিন্ন পোষাক বলে এই যে অভিন্ন বোকামিকে স্মার্ট করে প্রচার চলছে তার পেছনের অভিসন্ধিটি বুঝতে না পারাটাই বিপদ। গান্ধী রবীন্দ্রনাথ হয়ে বহুগুণীজন ‘এক’-এর গুণগান গেয়েছেন ঠিক। কিন্তু তাঁদের এক এর অর্থ আর আজকের কেন্দ্রগত হুঙ্কারের ‘এক’ আসলে এককথা নয়। একটি কথা সবসময়ের জন্য ‘এক’! এক ও সবসময় ভালো না। আলাদাও সর্বদা ভালো না। সে অর্থে এক ও মন্দ নয় অনেক সময়। আর আলাদা মানেই খারাপ নয় সর্বদা। এখানেই এসে পড়ে বিবেচনা। এখানেই যত বোঝাবুঝি। দেশ একটা মানে, একটা-মানুষ নিয়ে দেশ নয়। ১৪০ কোটি মন নিয়ে দেশ। তারা যেমন অনেক জায়গায় এক হবে, বহু জায়গায় ভিন্নও হবে। এক দেশ, এক প্রধান, এক নিশান, যদিও বা ভবিষ্যতে হয় কখনো, তাকে ভালোবাসার পথ ধরেই আসতে হবে। ঘাড় ধরে মানিয়ে নিলে কাজের কাজ হবে না। ঔদ্ধত্য, দম্ভেরই জয় হবে। আমার প্রতিবেশী এক রামভক্ত মানুষ বলছিলেন— ‘বড় ছেলে বৌ-বাচ্চা নিয়ে আলাদা হয়ে গেল বুঝলেন; এখন দেখছি এই ভালো হয়েছে, নিত্যদিনের খিটিমিটি ঝঞ্ঝাট তো নেই, আর কী বলব আপনাকে, সম্পর্ক আগের চেয়ে মজবুত হয়েছে।’ মনে হলো এইটা আসলে কথা, মানুষকে স্পেস দিয়েই মন মেলে। জোর করলে মেলে মনহীন ধড়!!
প্রেসি-বেথুনের সিলেবাস হিলি সীমান্ত কলেজে কী করে একই হবে, একথা আমার সঙ্গত কারণেই ঘটে ঢোকে নি। শহর কলকাতার পার্কস্ট্রিটে রাতভর নিত্যদিনের নাচাগানা নিয়ে মফস্বলের হা-হুতাশ আছে বলে শুনিনি। মাখনলালের দুই ব্যাটা একজন সাতফুটের কিছু বেশি। আর অন্যজন চার ফুট দশ ইঞ্চি পৌঁছতে পারেনি। তবে চার ফুট নয় এর তেজকে সমঝে চলত সাতফুট এক। মতাদর্শ যাচাই করলে তাদেরই একজন অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে, অন্যজন কড়া সমালোচক। আরো গভীরে গেলে দেখবেন একজন আলো বন্ধ করে ঘুমোতে পারতো না। অন্যজন আলোর ‘র’ দেখলেই রেগে জেগে উঠতো। তবু সাতফুট ঘুমিয়ে কুঁকড়ে গেছে দেখলে চারফুটভাই চাদর খানা লম্বুভাই এর গায়ে ঢেকে না দিয়ে ঘুমোতে পারেনি।
এখন অভিন্নের কথা যদি ভাবতেই হয়, তাহলে প্রথমত দেখতে হবে, মাখনের দুই ব্যাটা খোরাক মতো খেতে পায় কিনা, প্রয়োজন মতো নিরাপত্তা পায় কিনা, চিকিৎসা পায় কিনা, কাজ পায় কিনা, নিজেদের ভাষায় কথা কইতে পারে কিনা, পছন্দসই গান গাইতে পারে কিনা, দুই ভাইয়ের দেশ-কাল-জাতি-ধর্ম নিয়ে যা বোঝাবুঝি, তা নির্ভয়ে বলতে পারে কিনা! কর্তব্যকর্ম করে কিনা! দেশের কর্তব্য-কর্ম পায় কিনা! নাকি কেবল কর্তৃত্ব পায়!! ওদের পিঠে ছুরি দিয়ে চিরে ‘ভারত আমার ভারতবর্ষ’ কিংবা ‘একতাই বল’ লিখে দিলে ভারতের একতা আসবে না। মাখন কিংবা তার ব্যাটাদের ভালো হবে যে না, একথা বুঝতে অভিধান পাড়তে হয় না! যদি কিছু নোংরা ফূর্তি হয়, তা হবে সেই রক্ত-খেকো ছুরির! রাজনীতি দিয়ে ভাবলে ছুরি— মনের প্রভুর!
অনেক সময় ‘আলাদা’ খারাপ জেনেও জোর করে ‘এক’ এবং ‘অভিন্ন’ করা যায় না। যৌক্তিক অভিন্নকে কেন ওরা বুঝতে পারছে না?— সেই দায় নিতে হয় শাসককে। বলপূর্বক ভালো করতে গিয়ে বাবা যেমন নিজ সন্তানের প্রতি পাশবিক নির্যাতন চালাতে পারেন না, তেমনি তোমার ভালো করছি অতএব চুপটি করে থাকো, নইলে পিঠের চামড়া খুলে নেবো— এ একমাত্র পচা শাসকের অহং-ই বলতে পারে। আর মায়ের দু ঘা খেয়ে দুষ্টু ছেলে যে মায়ের আঁচল ধরে কাঁদতে-কাঁদতে দোষ স্বীকার করে তার কারণ মাতৃত্ব, অপত্য— এই সমর্পণ ঘায়ের কোয়ালিটির ওপর নির্ভর করে না! তর্কের খাতিরে যদি কোনো মা বাচ্চার উন্নতির জন্য চপেটাঘাতের ওপরই নির্ভর করেন, তবে সে মায়ের মাতৃত্বের কোয়ালিটি নিয়েই প্রশ্ন উঠবে।
পপুলিস্টরা যে সমানাধিকারের কথা বলে সে ‘বিপজ্জনক সমানাধিকার’। সমানাধিকার শব্দটির প্রতি প্রেমান্ধ হলে সে ফ্যাসিবাদের টের পাওয়া যায় না। বেশির ভাগ শিশু যেহেতু গেট খুলে লাগাতে ভুলে যায়, শিশুর ভোট থাকলে ওরা ‘বাগানের গেট খোলার অধিকার’-এর আইন আনতো। লেখা পড়া করতে গেলে যেহেতু ঘুম পায়, ব্রেনে চাপ পড়ে, তাই বেশিরভাগ বাচ্চারা ছুটি চায়, বাচ্চাদের ভোট থাকলে ‘মূর্খ থাকার অধিকার’-এর বিল আসতে দেরি হত না, বরং যে ছেলেমেয়েরা কষ্ট স্বীকার করে লেখা পড়া শিখতো তাদের কেই ডেপো বলা হতো। বলা হতো আলাদা, এই কতিপয় শিশুর জন্য ‘অশিক্ষার-সমানাধিকার’ আটকে যাচ্ছে, ওদের জাতীয় শত্রু হিসেবে দাগিয়ে দেওয়াও অসম্ভব কিছু ছিল না! এই ‘সমানাধিকার’ বিপজ্জনক। বিকেলে কেউ সিরিয়াল দেখেন, কেউ ‘ভিডিও-গেম’ খেলেন আর সেই বিকেলেই কতিপয় মানুষ আলাদা হয়ে ইথার-তরঙ্গ এর অর্থ বুঝতে চান, কেউ মাইক্রোস্কোপ-এ চোখ রেখে সেলের পচনের কারণ খোঁজেন। এই আলাদা শুধু আলাদাদের জন্য ভালো নয়, অভিন্নপন্হীদের জন্যেও মঙ্গলজনক!!
দেশে যখন সরকারি চোরের বাড়বাড়ন্ত। তখন সরকারের খাস লোক হয়ে চুরি না করলেই আলাদা। টাকাই যখন চিকিৎসা ব্যবস্থার মূল তখন সেবার হদিস পেলেই আলাদা। এসব আলাদা অভিন্নতার পক্ষে লাগে। রামের রহিমের ভালো করতে গেলে, রহিমের প্রতি সর্বাগ্রে দরকার ভালোবাসা ও সম্মানবোধ। রাম যদি রহিমকে বেজাত, বেজন্মা, কাফের মনে করে, তবে শত আইন এনেও মুশকিল আসান সম্ভব নয়। যারা অভিন্নতার গুণগান গান, তারাই আবার দীর্ঘদিনের অভিন্ন দুই শব্দ থেকে ভিন্নার্থ আবিষ্কার করেন, এবং করেন ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়ে। যেমন ধরুন ভারত এবং ইন্ডিয়া। এখন কথা চলছে অভিন্নতাও যথেষ্ট নয়, যেকোনো ‘একটা’ হতে হবে। একনায়কের একনায়ক-তন্ত্রের জেহাদ। যেমন আমার সরকারি নাম গৌরাঙ্গ। বন্ধু স্বজন গোরা বলে ডাকে। অন্যদিকে কনিষ্ঠ সন্তান বলে বাবা ডাকতেন ‘ছোটো’! সব নাম তুলে এক নামের তলায় নিয়ে আসতে, আমায় ‘ভারতচন্দ্র’ বলে ডাকলেই কি আর ছাতার মাথা আমি, কখনো ‘অন্নদামঙ্গল’ লিখতে পারব?
যাপিত নাট্যের পঞ্চদশ কিস্তি লিখলেন - কুন্তল মুখোপাধ্যায়

কুন্তল মুখোপাধ্যায়
সাহানার কলমে টানটান সাইকোথ্রিলার 'রক্তকরবী' - বৃতা মৈত্র





সমরেশ বসুর প্রজাপতি ও দুর্গরহস্য, কী হল এবং কেন হল? খোঁজ নিলেন বিতান দে





ব্যোমকেশ বক্সী আমার-আপনার মতোই একজন সাধারণ মানুষ, যিনি সত্যের অন্বেষণ করেন বলেই সত্যান্বেষী। ব্যোমকেশ এই বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনের অতি পরিচিত একটি টাইপ বা ধরন, তিনি কোনো অতিমানব নন। কিন্তু গোটা সিনেমা জুড়ে যা দেখলাম, তাতে ব্যোমকেশের ব্যোমকেশীয় সত্তার ছিঁটেফোঁটা নেই। চ্যালেঞ্জ-এর দেব এবং সত্যান্বেষীর দেব কখনোই এক হতে পারেন না। একজন অভিনেতার কাজই হল পৃথক পৃথক চরিত্রকে নিজের অভিনয়গুণে যথাযথ করে তোলার চেষ্টা করা। সেই জায়গায় যে দেব পুরোপুরি ব্যর্থ একথা বলাতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। উচ্চারণ একজন অভিনেতার প্রাথমিক কাজ বলেই আমি মনে করি। দেব বারবার বিভিন্ন মাধ্যমে জানিয়েছেন, তিনি নিজের উচ্চারণ নিয়ে যথেষ্ট ভাবিত এবং নিয়মিত উচ্চারণ সংশোধন করতে বহু অভ্যাস করেছেন ও করছেন। অথচ এই সিনেমাতেও সেই উচ্চারণের ত্রুটি বড্ড কানে লাগলো। আগেই বলেছি ব্যোমকেশ অতিমানব নন, কিন্তু গোটা সিনেমা জুড়ে ব্যোমকেশ যা যা করল, সবটাই প্রায় সুপারম্যানের মতন। শিবের মূর্তি সাজা থেকে এক হাতে সাপের গলা চেপে ধরা, কিংবা অপরাধীর পিছনে ছুটতে ছুটতে তার পকেটে থেকে বিষাক্ত পেন পরিবর্তন করে দেওয়া; কোনোটাই ব্যোমকেশকে ব্যোমকেশ করে তুলতে পারেনি। একই অভিযোগ অজিতরূপী অম্বরীশের ক্ষেত্রেও খাটে। অজিত যে বুদ্ধিমত্তার বাতাবরণে ব্যোমকেশকে সঙ্গ দেয়, বিরসার অজিত মোটেও তা নয়। এই অজিতের কনসার্ন কেবল খাওয়া-দাওয়া, মদের গ্লাস হাতে নিয়ে একটু গুণগুণ করা, আর সত্যবতীর মাথা ঠান্ডা করানো। কোনোভাবেই এটা আর যাই হোক, অজিত হতে পারে না। সুতরাং হলে দর্শকরা এলেন বাংলা সিনেমা দেখতে, টলিউডের সাময়িক খরা হয়তো কাটলও কিন্তু আর যাই হোক, ব্যোমকেশ হল না। ব্যোমকেশের ব্যকগ্রাউন্ডে সারাক্ষণ ‘ব্যোম ব্যোম সত্যান্বেষী’ প্রায় বিজিএমের মতন বাজতে থাকে যা অত্যন্ত বিরক্তির উদ্রেক ঘটানোর জন্য যথেষ্ট। অভিনয়ে ব্যোমকেশ ও অজিত ব্যতীত অন্যান্য ভূমিকায় রজতাভ দত্ত, রুক্মিণী মিত্র, শান্তিলাল মুখার্জি, সত্যম ভট্টাচার্য প্রমুখরা যথেষ্ট প্রশংসাযোগ্য অভিনয় করেছেন, কারণ ওই স্ক্রিপ্টে ওর বেশি আর কিছু করা যেত না বলেই মনে হয়। মূল চরিত্র হিসেবে সবচেয়ে হতাশজনক দেব এবং অম্বরীশ।
এর পাশাপাশি যদি সমরেশ বসুর প্রজাপতি সিনেমাটির চর্চায় আসি, শুরুতেই কিছু বাধার মুখোমুখি হতে হবে। কোন কোন জায়গায় এই সিনেমাটির সীমাবদ্ধতা তা আগেই কিছুটা জানিয়েছি, তার বাইরেও আরও কিছু কথা থেকে যায়। সুখেনের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় যেভাবে উপন্যাসে ধরেছেন সমরেশ বসু, ঠিক সেভাবেই চলচ্চিত্রের পর্দাতেও ধরার চেষ্টা করেছেন পরিচালক সুব্রত সেন। এক অশান্ত সময়ে সুখেনের জীবনে কোনো স্থিতি আসে না। বিঘ্নিত কৈশোর, যৌবন থেকে নতুন কোনো পাওয়ার প্রত্যাশা ছিল না সুখেনের কিন্তু তাও সে অবলম্বন হিসেবে শিখাকে পেয়ে যায়। সিনেমার একেবারে শুরুর দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়, ছৌ-এর মুখোশ পরে কয়েকজন অভিনয় করছে আর তার মাঝখান থেকে কিছু ভয়ংকর মুখোশ উঁকি মারছে। সমস্ত সাজানো জীবন তছনছ করে দেওয়াই যেন ওই মুখোশগুলির উদ্দেশ্য। এরপর বিভিন্ন পর্বে সুখেনের শৈশব, কৈশোর বা যৌবনের পর্যায়গুলো ধরা পড়েছে। সু্ব্রত দত্ত দেবের মতন জনপ্রিয় নন এবং স্টারডম বলতে যা বোঝায়, সেটিরও অধিকারী নন। যে চরিত্র বা সময়কে তিনি নিজের অভিনয়সত্তা দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে সবসময় মনে হয়েছে, উপন্যাসের সুখেনকেই বড়ো পর্দায় দেখা যাচ্ছে। একটি গল্প কতটা পরিশীলিত এবং নির্মেদ করা যায়, তার স্পষ্ট নিদর্শন হয়ে থাকবে সুব্রত সেন পরিচালিত এই সিনেমাটি। শ্রমিক ইউনিয়নের পলিটিক্স, ব্যক্তি জীবনের প্রেম এবং একজন গুণ্ডার শেষপর্যন্ত জীবনের কাছে হেরে অথবা জিতে যাওয়ার জবানবন্দি কীভাবে দু-ঘণ্টা সময়সীমার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হয়, তা দর্শকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন সিনেমাটি দেখলে। এই চলচ্চিত্রের কাছ থেকে ব্যবসায়িক সাফল্য ততটা আশা করা যায় না। একইসঙ্গে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও যে এর নির্মাণ তাও বলা যায় না। কিন্তু বর্তমানের সাপেক্ষেও একটি বিষয়কে কতটা প্রাসঙ্গিক করে তোলা যায় তা দেখিয়েছেন পরিচালক এবং কলাকুশলীরা; যেখানে সরাসরি নিজের জন্মের জন্য নিজেকে দায়ী না করে একজন প্রশ্ন তুলতে পারে। কাহিনির নাম কেন প্রজাপতি সে আলোচনার পরিসর আলাদা। এই সিনেমায় যে কটি গান ব্যবহৃত হয়েছে, আলাদা গান হিসেবে ধরলে কোনোটিকেই বিশেষ পছন্দ হবে বলে মনে হয় না, তবে কনটেক্সটের নিরিখে বিচার করলে বুঝতে পারবেন কেন এই ধরনের শব্দবন্ধ বা সুর ব্যবহার করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, টলিউডি সিনেমার বাতাবরণে যে রাজনীতির পরিসর তৈরি হয়, তাতে এই ধরনের সিনেমা ‘চলে’ না, অথচ নন্দনে তার প্রায় প্রতিটি শো-ই হাউজফুল। সু্ব্রত দত্ত বা ঋতব্রত মুখার্জি, শ্রীতমা দে বা মুমতাজ সরকার; অভিনয় কতটা যথাযথ হতে পারে চিত্রনাট্যের নিরিখে, তার পরিচয় এরা সকলে এবং অন্যান্যরাও দিয়েছেন।
সুতরাং প্রায় সমসময়ে, টলিউডের সিনেমা নির্মাণ এবং দর্শকদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন কীভাবে ঘটছে তার উদাহরণ হিসেবে এই দুটি সিনেমাকেই পাশাপাশি রাখা যেতে পারে। বাণিজ্যনির্ভর টলিউডি সিনেমা নাকি বাস্তবোচিত সময়ভিত্তিক কোনো পিরিয়ডিক কাহিনিকে আপনি বেছে নেবেন, সেই নির্বাচন সম্পূর্ণ আপনার। এই নির্বাচন পর্বেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, টলিউড ঠিক কেন বিপর্যন্ত। বিগত কয়েক মাসে ঠিক কোন কোন কারণে দক্ষিণী সিনেমা এত বিপুল পরিমাণ দর্শক টানতে পেরেছে এবং টলিউড পারেনি, তা এই দুটি সিনেমার পারস্পরিক পর্যালোচনা থেকেই আশা করি কিছুটা বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। ঠিক যে যে কারণে দেবের স্টারডম দুর্গরহস্যকে জনপ্রিয়তা দিয়েছে, সেই সেই কারণ না থাকার জন্যই প্রজাপতি জনপ্রিয়তা পায়নি। স্টারডমকে ব্যবহার করে একটা সময় পর্যন্ত দর্শক টেনে রাখা যায়, তারপর আবার পূর্বেকার পরিস্থিতি ফিরে আসে। ছোট্ট এই টলিউড ইন্ড্রাস্ট্রির অভ্যন্তরীণ জটিলতাও একটি বড়ো সমস্যার কারণ, সেই জটিলতার দ্রুত সমাধান না হলে ভবিষ্যতও খুব একটা বদলাবে বলে মনে হয় না। টলিউড তার দর্শকদের ফিরিয়ে আনতে পারবে কিনা তা সময় বলবে। বয়কট গ্যাং এখানে সক্রিয় নয়, কিন্তু একই সময়ে দুটি বাংলা সিনেমার সামগ্রিক প্রভাব, দৃষ্টিভঙ্গি এবং যৌক্তিকতা ঠিক কোন কোন ক্ষেত্রে কতটা কার্যকরী হয়ে উঠতে পেরেছে বা পারছে, তা আশা করি এই দুটি সিনেমার নিরিখেই স্পষ্ট। প্রবণতা একটি ইঙ্গিত মাত্র, বাকিটা বোঝার জন্য অপেক্ষা ভিন্ন উপায় নাই।
“কালীক্ষেত্র” থেকে কলিকাতা - অনুসন্ধানে কিশলয় জানা

।।কলকাতার গালগপ্পো।।
পর্ব ২
“কালীক্ষেত্র” থেকে কলিকাতা
“হে ‘কলিকাতা’, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ?”—এমন আবেগবিহ্বল প্রশ্ন যদি কেউ করে, তাহলে কলকাতা নিজে নীরব থাকলে কী হবে, প্রশ্নকর্তার আশেপাশে আমরা যারা আছি, তাদের সিংহভাগ বলে উঠবে, এ আবার একটা প্রশ্ন হল ? ‘কলকাতা’ এসেছে কালীক্ষেত্র থেকে। কালীঘাটের কালী ছাড়া আর কে-ই বা হতে পারে কলিকাতা নামের উৎস ? প্রশ্নকর্তা যদি এই উত্তরে আশ্বস্ত হন, তাহলে বলার কিছু নেই। কিন্তু তা না হয়ে তিনি যদি কৌতূহলী হয়ে নানা প্রশ্ন জুড়ে দেন তাহলেই বিপদ।
অধুনা যদিও বিশেষ কারণে কালীঘাট বলতে আমরা মা কালীকে না বুঝিয়ে অন্য কিছুকে বুঝি, কিন্তু এককালে কলকাতা বললেই কালীঘাট আর কালীঘাট বললেই মা কালীকে বোঝাতো। আদি গঙ্গার নাব্যতা যতদিন ছিল, পূর্ববঙ্গ থেকে শ’য়ে শ’য়ে তীর্থযাত্রী কালীঘাটে এসে পুণ্য অর্জন করে গেছেন। কলিকাতা আর কালীঘাটের কালী তাঁদের কাছে হয়ে উঠেছে সমার্থক। ফলে ‘কলিকাতা’ নামটির ব্যুৎপত্তি সন্ধান করতে গিয়ে অনেকেই এই মতকেই বিশ্বাস করে নিয়েছেন যে, কালীক্ষেত্র থেকেই কলিকাতা নামটির উদ্ভব। সেই ১৮৬০-এর পরবর্তীকাল থেকে কালীঘাট-কালীক্ষেত্র ও কলকাতার মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস শুরু হয়েছিল, আজও যার জের চলছে। ১৮৭৩ সালে জনৈক পদ্মনাভ ঘোষাল ক্যালকাটা নামের হ্যাণ্ডবুকে কলিকাতাকে একটি পুরাকালিক শহর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং বহুলা থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত অংশকে ‘কালীক্ষেত্র’ বলে দাবি করেছেন। পুরাণে না কি বলা হয়েছে এই সীমানার মধ্যে কোথাও সতীর “দক্ষিণ পদাঙ্গুলি” অর্থাৎ ডান পায়ের আঙুল পড়েছিল, সেই থেকেই এই স্থানের মাহাত্ম্য। এখন পদ্মনাভ কোন্ পুরাণ হাতে পেয়েছিলেন , তা তিনিই জানেন। উক্ত পুরাণের নামটি তিনি ইচ্ছে করেই যে উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলেন সন্দেহ নেই। একই কাজ করেছিলেন সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের বংশধর অতুল কৃষ্ণ রায় তথা এ. কে. রায় তাঁর বিখ্যাত ‘দ্য হিস্টরি অব ক্যালকাটা’ নামের বইতে, সেখানে তিনি ‘নিগমকল্পে’র পীঠমালার সাক্ষ্য দাখিল করে বহুলা থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত অঞ্চলের মধ্যস্থিত ত্রিভূজাকৃতি এক ক্রোশ তথা বর্তমান কালীঘাট যেখানে সেটিকে পবিত্র বলে উল্লেখ করেছেন। বোঝাই যাচ্ছে, এই সময় থেকেই কলিকাতা নামের সঙ্গে ধর্মীয় মহিমা যুক্ত করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এবং সুচতুর ভাবে একাধিক মানুষ এই গালগপ্পোটি ছড়িয়ে দিয়েছেন। অথচ কথাটির মধ্যে আদৌ কোন সত্যতা নেই, কারণ, প্রচলিত কোন পুরাণ—সে আদি হোক কিংবা অর্বাচীন, ‘কলিকাতা’র নাম কোথাও নেই। পীঠস্থানের বর্ণনাযুক্ত সর্বাধিক প্রাচীন পুরাণ ‘কালিকাপুরাণ’ কিংবা অর্বাচীন ‘দেবীভাগবত’—কোথাও না। একেবারে হাল আমলের কিছু তন্ত্রগ্রন্থে, যেমন ‘তন্ত্রচূড়ামণি’-তে সম্ভবত প্রথম কালীঘাট-কাহিনি ফলাও করে বলা হয়েছে।

অথচ প্রাচীন কাল থেকে যদি কালীক্ষেত্র হিসেবে এর স্থান-মাহাত্ম্য থাকত, তা হলে স্থানটি এত তুচ্ছতার সঙ্গে মোঘল আমলে হোক কিংবা নবাবী আমলে, কিংবা কোম্পানির পেপারস্-এ উল্লেখিত হতো না। গোবিন্দপুর-সুতানুটির জায়গায় কলিকাতাই হয়ে উঠত কেন্দ্রবিন্দু এবং তাহলে হয়তো এই গ্রাম তিনটির ( কিংবা দুটি ) নিঃশুল্ক পাট্টা পাওয়া ইংরেজদের কাছে এত সহজ হতো না। কারণ, নবাব কোন মূল্যেই তীর্থক্ষেত্র আছে, এমন কোন স্থান নিঃশুল্ক পাট্টা দেবেন না, তাতে নবাবের রাজস্বের ক্ষতি। তীর্থকর হিসেবে পাওয়া মূল্য তো কম ছিল না। কিন্তু তা-ও নবাব এই স্থানটি দিতে আপত্তি করেন নি, তার কারণ, তখনো এখানে কালীঘাট নামক কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না এবং জঙ্গলাকীর্ণ ম্যালেরিয়া-সঙ্কুল এই প্রায় পরিত্যক্ত স্থানটি যদি এই সুযোগে ইংরেজদের হাতে বসবাসযোগ্য হয়ে ওঠে, তাতে নবাবেরই লাভ, এমন ভাবনা তাঁর মাথায় এসেছিল এবং তাতেই ইংরেজদের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছিল। আরো উল্লেখযোগ্য যে, এমন কোন তীর্থমাহাত্ম্যযুক্ত স্থানের পাট্টা লাভ করলে তা সাড়ম্বরে উল্লেখের সুযোগ ছাড়তেন না কোম্পানির কর্মকর্তারা। কিন্তু কোম্পানির প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজে কোথাও কালীঘাটের নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই। অথচ ১৮৬০-এর পরবর্তীকালে পৌঁছে দেখতে পাই, কালীঘাট একেবারে রমরম করছে তীর্থক্ষেত্র হিসেবে—পাণ্ডা-বেশ্যা-ফড়ে-নেশা

কেউ কেউ ‘কালীঘাটা’ থেকে কলিকাতা নামটির উদ্ভব বলেছেন। এই মতের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মাইকেল মধুসূদনের প্রাণপ্রিয় বন্ধু গৌরদাস বসাকের লেখায়। ‘ক্যালকাটা রিভিউ’-তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে অবশ্য তিনি এ-কথাও বলেছেন যে, হিন্দুর আরাধ্য দেবী কালীর সঙ্গে কলিকাতার যোগ থাকতে পারে না, কারণ স্বাভাবিকভাবেই দেবীর নামের বিকৃতি তাঁরা কেউ মেনে নেবেন না। যদিও, এই মতের বিপক্ষে বলা যেতে পারে, যে বাঙালি কৃষ্ণ🡪কাহ্ন🡪কানু মেনে নেয়, তাদের পক্ষে কালী থেকে কলি মেনে নেওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। তাঁর মতে, কালী ঘাট্টা থেকে কলিকাতা শব্দটি আসতে পারে। কারণ, আগে গোবিন্দপুর অঞ্চলে একটি কালীমন্দির ছিল, যেখানে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষজন আসতেন এবং নির্দিষ্ট ঘাটে নামতেন, যেটিকে তাঁরা কালী ঘাট্টা বলতেন, সেই থেকেই কালীঘাট শব্দটি এসেছে, তার থেকেই পরবর্তীকালে কলিকাতা নামটির জন্ম। মনে রাখতে হবে, গৌরদাস বসাক যা তাঁর লেখায় বলেছেন, তা কিন্তু কোন আদি উৎস দ্বারা স্বীকৃত নয়। যে ‘ভবিষ্যপুরাণে’র সাক্ষ্য তিনি উদ্ধার করেছেন এবং কোন কোন গবেষক তা মেনেও নিয়েছেন, তাঁরা ভুলে যান, ‘ভবিষ্যপুরাণ’ লেখা হয়েছে নেহাতই অর্বাচীনকালে। এর সাক্ষ্য কোন মতেই কালীঘাটের প্রাচীনত্বের প্রমাণ নয়।
আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা কবিরাম-এর ‘দ্বিগ্বিজয় প্রকাশে’ পুরাণের আদলে কল্পিত গালগপ্পের শেষে তিনি “কিলকিলা” নামক দেশ তৈরির কথা বলেন এবং তার চারপাশের গ্রাম হিসেবে হুগলী, বাঁশবেড়িয়া, ভাটপাড়া, খড়দহ, শিয়ালদহ ইত্যাদি অঞ্চলের নাম করেন। রাধাকান্ত দেবও এই মতের সমর্থনে শেষ জীবনে বৃন্দাবনে বাসকালীন লেখা বাংলা স্তবমালায় “কিলকিলা” নামটি গ্রহণ করেছেন। বলা বাহুল্য, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকেই যে অঞ্চলগুলির দুর্দশা ছিল সীমাহীন, ষোড়শ শতকে সেই স্থানগুলির অবস্থা কেমন হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। অতএব কালীর কেল্লা বা মন্দির থেকেও কিলকিলা আসেনি। আর কিলকিলা থেকেও কলিকাতা নামের জন্ম হয় নি। বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের অর্বাচীন কাব্যটির উল্লেখ থেকে আমরা এখানে বিরত থাকলাম, কারণ, কাব্যটি রাম না হতেই রামায়ণের মতো এমন অনেক স্থানের নাম উল্লেখ করেছে যে, তার প্রামাণিকতা নিয়েই সংশয়ের অবকাশ থেকে গেছে।
সপ্তদশ শতাব্দীর কবি চট্টগ্রাম-নিবাসী সৈয়দ আলাওলের “পদ্মাবতী”র একটি পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠায় কলকাতাকে উল্লেখ করা হয়েছে ‘কলঘাট্টা’ হিসেবে। পাণ্ডুলিপিটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পুথিসংগ্রহ বিভাগে রক্ষিত আছে। এই নামটি অনুযায়ী যাঁরা কলিকাতা নামের উৎপত্তির কথা ভাবেন, তাঁরাও ভুলে যান যে, পুথিটির লিপিকালের প্রাচীনতা সম্পর্কে কিন্তু পণ্ডিতদের মৌখিক অনুমান-প্রমাণ ছাড়া কোন বিজ্ঞানসম্মত টেস্ট করা হয় নি। পুথিটি পরবর্তীকালে লিপিকৃত হয়ে থাকলে, ‘কলঘাট্টা’ শব্দটির আর কোন মূল্য থাকে না। দীনেশচন্দ্র সেন অবশ্য ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে লেখা প্রবন্ধে প্রায় একশো বছর আগে পুথিটি লিপিকৃত হয়েছিল বলে অনুমান করেছেন। যদিও তাতেও সালটি ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের আগে নয়। ততদিনে কালীঘাটের রূপকল্প জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কলিকাতাকেও মহিমান্বিত করার কৌশলী প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছে, কারণ তা না হলে ভারতবর্ষের রাজধানী হিসেবে কলিকাতার জাত থাকে না। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কোম্পানির নথিপত্রে যাঁরা “Kalghatta” কথাটা পান এবং মনে করেন এইটিই তবে আজকের কলকাতার পূর্ব নাম, তাদের দু’টি মজার গালগপ্পো শোনাই। দু’টি গপ্পোই আপনাদের শোনা, যারা নেহাতই শোনেন নি, তাঁদের জন্যই দেওয়া। এই দুটি গপ্পো শুনে বুঝতে পারবেন, ইংরেজদের দেশীয় ভাষাজ্ঞান ঠিক কেমন ছিল।
প্রথম গপ্পোটি হল, যে প্রথম সাহেব মানুষটি জাহাজ থেকে এই অঞ্চলে প্রথম পা রেখেছিলেন, তিনি দেখলেন, দুইজন স্থানীয় লোক একটি কাটা গাছের কাছে বসে আছে। তা সাহেব জানেন না, তিনি কোন্ জায়গায় এসেছেন।
তিনি স্বাভাবিকভাবেই তাদের স্থানটির নাম জিজ্ঞাসা করলেন। তারা ভাবল, সাহেব গাছটি কবে কাটা হয়েছে, সেটাই জিজ্ঞাসা করছেন, অতএব তারা জবাব দিল, কাল কাটা ! এর থেকে সাহেবটি ধরে নিলেন স্থানটির নাম—ক্যালকাটা।
সাহেবটির বাংলাজ্ঞান নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের ‘মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত’ পড়েছেন, তাঁরাই জানেন, উনিশ শতকের শেষ দিকেও তাঁদের বাংলাজ্ঞান কেমন ছিল। কিন্তু এই গালগপ্পোটির একটি মারাত্মক ভ্রান্তি আছে। বাঙালি দুজন সাহেবের প্রশ্নটি অনুমানে বুঝে উত্তর দিয়েছে, তা মেনে নিলাম তর্কসাপেক্ষে। কিন্তু উত্তর দিতে গিয়ে তারা বাংলায় না বলে হিন্দুস্থানীতে বলল কেন ? হিন্দুস্থানী ভাষা সচরাচর বাঙালিরা উচ্চারণ করবে তখন, যখন তাদের সংস্পর্শে তারা বসবাস করবে। কলকাতার তখন যা অবস্থা, সেখানে হিন্দুস্থানী দূরের কথা, বাঙালিই ক’ ঘর ছিল, তাতে সন্দেহ আছে। আর এখানে তারা সাহেবকে হিন্দুস্থানীতে উত্তর দিল, এটাই আশ্চর্যের।
দ্বিতীয় গপ্পোটি একটু অন্যরকম। শুনিয়েছেন, ‘কলিকাতার কথা’ খ্যাত প্রমথনাথ মল্লিক। তখন কালিকট থেকে বিতাড়িত হয়ে তখন ইংরেজরা এসে পড়েছে কলিকাতায়। এদিকে ততদিনে ইউরোপে কালিকটের জিনিসের খুব কদর। ‘মেদ ইন কালিকটে’র পরিবর্তে ‘মেড ইন কলিকাতা’ দেখলে সে জিনিস আগের মতো আর বিক্রি না-ও হতে পারে। আমরা বাঙালিরা যেমন ধূপ কিনতে গেলে ‘মেড ইন কলকাতা’ দেখলে নাক সিঁটকাই, ‘মেড ইন বেঙ্গালুরু’ খুঁজি, তেমনই আর কী ! তা ইংরেজ ব্যবসায়ীরা গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলেন। তারপর তাঁদের মধ্যে একজন সমাধান বাতলে দিলেন। সব প্যাকিং বাক্স নামিয়ে তাতে তিনি কালিতে ব্রাশ ডুবিয়ে লিখে দিলেন “Made in KALKATA”, এক ঝলকে দেখলে কালিকট বলে মনে হতে পারে, অতএব জন্ম নিল ‘কলকাতা’র নাম। বলা বাহুল্য, এই সব গল্প একেবারেই গালগপ্পো, অধমের এই রচনার মতো। এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, গ্রহণযোগ্যতাও নেই। তবে, বড় কথা হল, এই জাতীয় গল্পে কোথাও কালীক্ষেত্র হিসেবে কলিকাতা নামটির জন্ম, এমন মিথের বিপরীত কথাই আছে। নেহাতই ভ্রান্তিবশত কিংবা ব্যবসায়িক কৌতূহলবশত একটি স্থানের নাম তৈরি হওয়ার গল্প আছে।

বলা বাহুল্য, কোন গল্পই বিশ্বাসযোগ্য নয়, কারণ আদতে সেগুলি “গপ্পো”। কারণ, তাহলে একটা সঙ্গত প্রশ্ন উঠে আসে ; যদি এমনটাই হয়, তাহলে তো কলিকাতা নাম জন্মানোর আগে এই অঞ্চলের অন্য কোন নাম ছিল, সেটি কী ? এখান থেকেই মনে হয়, কালীঘাট ও কলিকাতার যোগ নেহাতই আকস্মিক। তার চেয়ে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত, রাধারমণ মিত্র মহাশয়ের শত চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। কারণ, রাধারমণ বাবুর অজ্ঞতা পরবর্তীকালে তারাপদ সাঁতরার মতো প্রথিতযশা গবেষক যুক্তিসহ খণ্ডন করেছেন। তবে তারাপদ সাঁতরার মতও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। তিনি আমপোতা🡪আমতার সাদৃশ্যে কলকেপোতা🡪 কলিকাতা—বলে গ্রহণ করেছেন এবং জানিয়েছেন, নদী-তীরবর্তী কোন কলকে ফুলের গাছকে কেন্দ্র করে গ্রামের পত্তন হয়, সেই থেকে কলকেপোতা নাম ক্রমশ অন্তস্বরের প্রথমাংশের লোপের ফলে কলকাতায় দাঁড়ায়। কলকে গাছকে কেন্দ্র করে গ্রামের উৎপত্তি এবং কলিকাতা নামের উদ্ভব, এটিও সুকুমার সেনের আরবী Quli অর্থাৎ নির্বোধ এবং Qatte অর্থাৎ দস্যু, হত্যাকারী তথা বজ্জাত—বোকা বজ্জাতের আড্ডাখানা অর্থে কলিকাতা নাম জন্মানোর গপ্পের মতোই দুর্বল। বরং, সুনীতিবাবু যুক্তিসহ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তার জোর বেশি। তিনি বর্তমান ‘কলকাতা’ ছাড়াও আরো দুটি কলিকাতার সন্ধান পেয়েছিলেন—একটি হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত রসপুর-কলকাতা, অন্যটি ঢাকা জেলার অন্তর্গত কলকাতা। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল, কলি অর্থাৎ কলিচুন এবং কাতা অর্থাৎ শামুকপোড়া, শামুক-ঝিনুক পুড়িয়ে এই অঞ্চলে কলিচুন প্রস্তুতের কাজ হত, সেই থেকে কলিকাতা নামটির জন্ম। অর্থাৎ, কালীক্ষেত্র কালীঘাটের সঙ্গে কলিকাতা নামের কোন যোগ নেই, ওটি বিশুদ্ধ গুল্প ( গুল + গল্প )।
(চলবে )
সাধারণ দর্শকের নজরে সাধারণ রঙালয়ের ১৫০ বছর ও গ্রুপ থিয়েটারের ৭৫ বছর- মৃণালকান্তি দাস
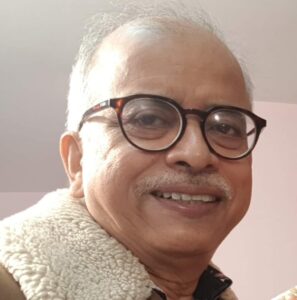
মৃণালকান্তি দাস
সাধারণ রঙ্গালয়ের ১৫০ বছর আর গ্রুপ থিয়েটারের ৭৫ বছর উদযাপিত হচ্ছে এবছর। সাধারণ রঙ্গালয় বা ব্যবসায়িক থিয়েটারের সাথে আমার পরিচিতি সামান্য দু একটি নাটক দেখার মাধ্যমে। আমার কলেজ জীবনের সময় ব্যবসায়িক থিয়েটারে দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য ছিল ক্যাবারে নাচের ছড়াছড়ি, আর ছিল সিনেমার পরিচিত মুখকে নিয়ে থিয়েটার করানোর একটা প্রবণতা। এর মধ্যে নাটকের বিষয়, প্রয়োগ ও শৈল্পিক উপস্থাপনায় ব্যতিক্রমী ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ওনার বোর্ডের নাটক দেখেছিলাম ‘নামজীবন’ আর অন্যান্য বোর্ডের নাটকের মধ্যে দেখেছিলাম গ্ল্যামার ও ক্যাবারের সমন্বয়ে ‘আসামী হাজির’ । বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস থেকে জানা যে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয় করে সাধারণ রঙ্গালয়ের উদ্বোধন হয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের হাত ধরে। সেই সাধারণ রঙ্গালয় পর্যায়ক্রমে ব্যবসায়িক থিয়েটারে পরিণত হয়েছিল, যে থিয়েটার একসময় হাতিবাগানের বিভিন্ন মঞ্চে রমরমিয়ে চলতো, সেই থিয়েটার এখন সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত। শুধু যৌনতা আর পর্দার গ্ল্যামার দেখিয়ে শিল্পের শর্ত পূরণ হয় না, দর্শকদের মনোরঞ্জনও হয় না। দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্যের থিয়েটার কীভাবে ব্যবসায় অধিক মুনাফার খপ্পরে পণ্য হয়ে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল সে সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা বিশ্লেষণ হতে পারে।
আমি ৭০ এর দশকে যে সময় নাটক দেখা শুরু করি সেটা মূলতঃ গ্রুপ থিয়েটারের নাটক। যে নাটক আমার শিল্প চেতনায় শান দিতো, আমার জীবনের রাজনৈতিক ভালোবাসায় ইন্ধন যোগাতো।
গ্রুপ থিয়েটার সম্পর্কেও জানা যে গ্রুপ থিয়েটারের সূত্রপাত ধরা হয় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে বহুরূপীর নবান্ন অভিনয় দিনটিকে। তার আগেই অবশ্য ১৯৪৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলন মঞ্চ থেকে পি সি যোশীর নেতৃত্বে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ তৈরি হয়েছে। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর নভেম্বরে সারা দেশকে কাঁপিয়ে দিয়েছে গণনাট্য সঙ্ঘের নবান্ন। যে নাটক লিখেছিলেন বিজন ভট্টাচার্য আর পরিচালনা করেছিলেন যুগ্মভাবে বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্র। অভিনয় করেছিলেন তৃপ্তি ভাদুড়ি, শোভা সেন, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান প্রমুখ। তিন চার বছরের মধ্যেই সেই গণনাট্য থেকে বেরিয়ে এসে শম্ভু মিত্ররা বহুরূপী নাট্যদল তৈরী করে মঞ্চস্থ করলেন নবান্ন। গণনাট্য থেকে বেরিয়ে এলেন বিজন ভট্টাচার্য। তৈরি করলেন ক্যালকাটা থিয়েটার। পরবর্তী কালে প্রথমে গণনাট্যে যোগ দিয়েও বেরিয়ে এসেছিলেন উৎপল দত্ত, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়ের মতো দিকপাল নাট্যব্যক্তিত্বরা। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ থেকে বেরিয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ থিয়েটারের দল তৈরির কারণ নিয়ে অনেক তর্ক বির্তক থাকলেও গণনাট্যের রাজনৈতিক আদর্শ নিয়েই দু- একজন ব্যতিরেকে সবাই গ্রুপ থিয়েটারের নামেই নাটক করতে থাকলেন এ নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। তারা প্রয়োজন মনে করেছিলেন প্রকাশ্যে রাজনীতির চর্চাকে থিয়েটারের আঙিনায় নিয়ে আসার। নাটক শুধু বিনোদন নয় শ্রেণি সংগ্রামের তীক্ষ্ণ হাতিয়ার। তারা মনে করতেন নাটক মানেই আন্দোলন- তার মানেই প্রগতিবাদী। নাটক তথা শিল্প সংস্কৃতির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ সাধন – এটাই শিল্পের কাজ, এটাই শিল্পীর কাজ। দ্বিতীয় আর একটি ধারার নাটকও সেইসময়ের নাট্যপ্রবাহে শুরু হয়েছিল। সেটা হলো ভালো নাটক ভালো করে করতে হবে যাতে সমাজটা একটু ভালো হয়। ভালো নাটকের দর্শক তৈরি করতে হবে। প্রথম ধারার নাটকের প্রতি এদের অভিযোগ ছিল যে ওটা শিল্প নয়, propaganda. সরাসরি বলা ভালো দুটি ধারার সমাজ সচেতন নাটক চালু ছিল যাঁরা সাংস্কৃতিক আন্দোলন বা বিপ্লবকে রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রারম্ভিক কাজ মনে করতেন। নবনাট্য – সৎনাট্য এই নামে দ্বিতীয় ধারার নাটক করা শুরু হলেও কালক্রমে সবই গ্রুপ থিয়েটার নামেই সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিতি পায়। ৬০ এর দশকে বাংলায় বহু গ্রুপ থিয়েটারের সৃষ্টি হয়। এই থিয়েটারে অগ্রণী ভূমিকা নেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। এই থিয়েটারের সঙ্গে পড়াশোনার একটা যোগাযোগ ছিল। নাট্যকর্মীদের জানতে হতো সারা পৃথিবীতে কি হচ্ছে, দেশে কি হচ্ছে, চারপাশে কি হচ্ছে। জানতে হতো সমাজের জ্বলন্ত সমস্যার কথা। নাটক হৃদয়ের থেকে মস্তিষ্কে নাড়া দিতো বেশি। চিন্তা করতে হতো, ভাবতে হতো। ঋত্বিক ঘটক বলতেন- ভাবো ভাবো, ভাবা প্র্যাকটিস করো। ছিল শৃঙ্খলা, কঠোর অনুশীলন, ছিল চরম পেশাদারিত্ব অথচ অব্যবসায়িক। প্রায় সমস্ত দলই পরিচালকের নেতৃত্বে দলগতভাবে কাজ করতেন এবং দলের অনেক সদস্যেরই অর্থোপার্জনের স্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় আদর্শ ও ভালোবাসার টানে নিজেদের পকেটের টাকায় নাটক করে গেছেন। নাটক করে উপার্জন করার প্রশ্ন তখনও ওঠে নি। সেই সময়ের বহু নাটকের জনপ্রিয়তা ও দর্শকও ছিল অনেক। বহু নাটকের বহু শতাধিক অভিনয়ও মঞ্চস্থ হয়েছে। ৭০-৯০ এর দশকের অনেক অনেক নাটক কয়েকশো অভিনয় হয়েছে। মারীচ সংবাদ, জগন্নাথ, চাক ভাঙা মধু, নরক গুলজার, ফুটবল, বেলা অবেলার গল্প, সাজানো বাগান, টিনের তলোয়ার, ব্যারিকেড এরকম অনেক নাটকের নাম করা যায় যেসমস্ত নাটক কয়েক শত অভিনয় হয়েছে। কিছু নাটক এমন জনপ্রিয় হয়েছিল যে সহস্রাধিক অভিনয় হয়েছে। তবুও মনে হয় সমাজের সর্বস্তরে বিশেষ করে শ্রমিক , কৃষক ও গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে গ্রুপ থিয়েটার সেভাবে পৌঁছতে পারেনি। যা কিনা পেরেছিল গণনাট্য সংঘ ও বাংলার নিজস্ব লৌকিক নাটক যাত্রা। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ ষাটের দশকের যাত্রায় ভক্তিরসের পালার স্থান নিতে শুরু করে সামাজিক রাজনৈতিক পালা। উৎপল দত্ত সেইসময়ে বহু রাজনৈতিক যাত্রা পালা লেখেন। উনি মনে করতেন যাত্রার মাধ্যমে বহু সাধারণ মানুষের কাছে সমাজ পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে পৌঁছানো যাবে। গ্রুপ থিয়েটার কখনোই সাধারণ আম জনতার থিয়েটার ছিল না। কলকাতা ও কিছু কিছু জেলার শহরে গড়ে ওঠা গ্রুপ থিয়েটারের নাটক দেখতে গ্রাম ও শহরতলীর আগ্রহী সচেতন দর্শককে কলকাতায় বা জেলার শহরে আসতে হতো। নাটকের মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে শ্রমিক কৃষকের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তার প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে একটা সীমাবদ্ধতা ছিল। প্রায় সব নাটকের দর্শকের মধ্যে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রাধান্য ছিল। শ্রমিক কৃষক শ্রেণির মধ্যে গ্রুপ থিয়েটারের প্রভাব ছিল বেশ কম। গ্রামে গঞ্জে শ্রমিক কৃষকের মধ্যে সহজ কথায় পরিবেশিত গণনাট্যের প্রভাব ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি। সে প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হতে পারে তবে এই আলোচনা গ্রুপ থিয়েটারের ৭৫ বছরে এখন থিয়েটারের ভূমিকা। বর্তমান সময়ে নাটকের দলের সংখ্যা, প্রতিদিন বিভিন্ন মঞ্চে নাটক অভিনয়ের সংখ্যা, নিয়মিত নাট্যকর্মীর সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু খুব ভালো লাগা নাটকও কিছু অভিনয়ের পরে আর দর্শক পাচ্ছে না। এখন একটা নাটকের ৫০ তম অভিনয় হওয়া মানে একটা বিরাট ব্যাপার। গত ১০-১২ বছরের মধ্যে হওয়া সেরা নাটকগুলোও ৫০ টা অভিনয় হয়েছে কি না নিশ্চিত নই। তার আগের ১০-১২ বছরে হওয়া নাটকগুলোর মধ্যে কিছু নাটক হয়তো ১০০ তম অভিনয় হয়েছে। তার মানে সামগ্রিক ভাবে নাটকের দর্শক কমছে। নাটকের মান যে খারাপ হচ্ছে সে কথা বলা যাবে না। তবে দর্শক হচ্ছে না কেন? একটা কারণ অবশ্যই মনে হয় নাটকের টিকিটের দাম। আমি প্রথম যে সময়ে নাটক দেখি ৭০ এর দশকে তখন টিকিটের দাম ছিল ১-১০ টাকা। ৯০ এর দশকেও সর্বোচ্চ টিকিটের দাম ১০ টাকা থেকে ২৫ টাকা অনেকদিন অবধি ছিল। অনেক সাধারণ মানুষ, ছাত্র- ছাত্রীদের নাগালের মধ্যে। তারপর দীর্ঘদিন টিকিট ১০০ টাকার মধ্যে ছিল। এখন কিছুদিন যাবৎ দেখছি সর্ব নিম্ন টিকিটের দাম ১০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৩০০-৫০০ টাকা প্রায় সব নাটকের। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এতো দাম দিয়ে টিকিট কেটে বেশি নাটক দেখতে পারে বলে মনে হয় না। এখন নাটক দেখতে গিয়ে দর্শকদের মধ্যে তরুণ ছেলেমেয়েদের দেখা যায় খুব কম। যাদের দেখা যায় তারা হয়তো কোন নাট্যদলের কর্মী। এই যে একটা মঞ্চ সফল নাটকও খুব বেশি অভিনয় হচ্ছে না এর কারণ খোঁজা দরকার। কিছু দল টিকিটের দাম বাড়িয়ে আর্থিক ভাবে পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। একটা খুব খরচের প্রযোজনা মানে নামী দামী অভিনেতা আছে সেরকম একটা নাটকের হাউসফুল শোয়ে, যেখানে টিকিটের দাম ১০০ ( সামান্য কয়েকটা)- ৫০০ টাকা, বড় প্রেক্ষাগৃহে টিকিট বিক্রি হতে পারে দেড় থেকে দুলক্ষ টাকা। স্বাভাবিক কারণেই সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না নাটকটা দেখার। কিন্তু সেই গুটি কয়েক দল কয়েকটা শো করেই প্রযোজনা খরচ তুলে ফেলছে। তাদের টার্গেট দর্শক হচ্ছে সমাজের আর্থিকভাবে সচ্ছল কিছু নাট্যমোদী মানুষ। এছাড়াও আছে চেনা জানা পারস্পরিক নাট্য উৎসবের বহুমূল্যের আমন্ত্রিত অভিনয়। আছে বিভিন্ন রকম সরকারি অনুদান ও উৎসব। যার ফলে সেই নাটকের দলগুলো খুব একটা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে না। কিন্তু সাধারণ দর্শকের বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের নিয়মিত নাটক দেখার অভ্যেসটা তৈরি হচ্ছে না । ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলা নাটক, নাট্য আন্দোলন ও তার সাথে জড়িত নিয়মিত নাট্যচর্চায় থাকা আর্থিক ভাবে দুর্বল নাট্যদলগুলি।
আমার প্রথম দেখা নাটক মারীচ সংবাদ, তারপরই জগন্নাথ। রাজেশ খান্নার সিনেমা ওপেনিং ডে ওপেনিং শো দেখা আমি এক অন্য স্বাদের শিল্পে আকৃষ্ট হলাম। নাটকের নেশায় পেয়ে বসলো। আমার মতোই কতো নতুন ছেলে মেয়ে সেইসময় শিল্পের টানে, রাজনৈতিক আদর্শের টানে শহরাঞ্চল থেকেও নাটক দেখতে আসতো। মারীচ সংবাদ দেখে সেই যে আমি বুঝলাম সাম্রাজ্যবাদ কাকে বলে সেই বোঝা-ই এখনো রয়ে গেছে। সেই সময়কার গ্রুপ থিয়েটারের সব নাটকই গ্রুপ, নাটককার ও পরিচালকের নামে উপস্থাপিত হতো। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি নাট্যকর্মীদের রুজিরোজগার এর একটা বাস্তব সমস্যা আস্তে আস্তে গ্রুপ থিয়েটারের ওপর প্রভাব ফেলতে থাকে। জীবিকার প্রয়োজনেই অনেক নাট্যকর্মীকে থিয়েটারের আঙিনা ছেড়ে চলে যেতে হয়। ৮০ এর দশকের শেষ দিকে নাটককেই জীবিকা করার লক্ষ্যে সর্বক্ষণের নাট্যকর্মী হবার একটা প্রবণতা কিছু কিছু নাট্যকর্মীর মধ্যে দেখা দিতে থাকে। সময়ের সাথে সাথে গ্রুপ থিয়েটার ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হতে হতে আজকের থিয়েটারে রূপান্তরিত হয়েছে। ৯০ এর দশকের পর থেকে বিশ্বায়নীভবনে সমাজটা দ্রুত বদলে গিয়েছে। ভোগবাদ মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। অর্থনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা ক্রমশ গৌণ হয়ে যাচ্ছে। তার প্রতিফলন থিয়েটারেও পড়ছে। পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক বাতাবরণ পরিবর্তনের ছাপও থিয়েটারের ওপর স্বাভাবিক কারণে পড়ছে। গণনাট্য থেকে বেরিয়ে এসে যে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে গ্রুপ থিয়েটারের সৃষ্টি হয়েছিল সেই দৃষ্টিভঙ্গি আজ পাল্টে যাচ্ছে। দোষ কারো নয়। যে ব্যবস্থাটা পরিবর্তনের জন্য ৭৫ বছরের নাট্য আন্দোলন সেই আন্দোলনটাকেই বিশ্বায়ন পরবর্তী ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থা গ্রাস করে ফেলছে। এখন বহু বহু নাটকের দল তৈরি হচ্ছে। অনেক অনেক ছেলে মেয়ে নাটক করতে আসছে। অনেকেই শুধু নাটকই করেন। নাটককেই জীবিকা করতে চাইছেন। নাটকের শিক্ষা কোথায় কীভাবে হচ্ছে জানি না। অনেকেই ইচ্ছা পোষণ করছেন কোম্পানি থিয়েটার করেই বাড়ি গাড়ি করবেন। যদি সেটা সম্ভব হয় তাহলে খুবই আনন্দের কথা। তবে বিষয়টা অর্থনীতির। নাটকটাকে প্রোডাক্ট হিসাবে ধরে কাস্টমারের চাহিদা অনুযায়ী তৈরি করে ব্যবসা করতে হবে। তবে তো নাট্যকর্মীদের রোজগার হবে। সারা পৃথিবী জুড়ে সমস্ত ক্ষেত্রে যেভাবে কর্পোরেট দুনিয়ায় বড় বড় রাঘব বোয়ালেরা ছোট ছোট কর্মক্ষেত্রগুলিকে গ্রাস করে ফেলছে, নাটকের ক্ষেত্রেও সেই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। বিশেষ বিশেষ কিছু মুখকে ভাড়া করে দলবিহীন বহু অর্থ ব্যয়ে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নাট্য প্রযোজনা করে দর্শক টানার চেষ্টা চলছে। তবুও দু একটি ক্ষেত্র ছাড়া কোন নাটক সেরকম জনপ্রিয় হচ্ছে না। দর্শকদের চাহিদা মেটাতে পারছে না। নতুন প্রজন্মকে থিয়েটার দেখতে আগ্রহী না করতে পারায় সামগ্রিক ভাবে থিয়েটারের ক্ষতি হচ্ছে। সামগ্রিক ভাবে বাংলার নাট্যসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে বাংলার নাটকের দর্শক তৈরি করার কাজে। আরো বেশি দর্শকের কাছে নাটক যাতে পৌঁছাতে পারে সেই চেষ্টাটা করা দরকার। নাটকের প্রযোজনা খরচ যতটা সম্ভব কম করে সব জায়গায় সবার জন্য যাতে মঞ্চস্থ করা যায় সেই কথাটা মাথায় রাখতে হবে। অনেকেই বলবেন শিল্পের প্রয়োজনে কোনরকম আপোষ করা যায় না। তাহলে দর্শককে নাটক দেখতে নিয়ে আসার জন্য কিছুটা আপোষ করুন। নাটককে কিছু মানুষের মধ্যে রাখবেন না সমাজে বিস্তৃত করবেন সেটা ঠিক করার দায়িত্ব নিয়ে নাটক করুন এটা অনুরোধ। বর্তমান সময়ে কটা নাটকের শতাধিক অভিনয় হয়েছে খুঁজে দেখতে হয়। নাটকের টিকিটের দাম সাধারণের বিশেষত আগামী প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের নাগালের মধ্যে রেখে নাটক প্রযোজনায় আগ্রহী হোন। পরিচিত মুখ দেখিয়ে নাটক করানোতে নাটকের জন্য নতুন দর্শক তৈরি হচ্ছে না। মুখ দেখার ভীড় হচ্ছে নাটক দেখার নয়। নাটকের দর্শক তৈরি না হলে সেটা নাটকের ভবিষ্যতের পক্ষে খুবই খারাপ। নাটকের দল বাড়ছে, নাটক করার আগ্রহী কর্মী বাড়ছে কিন্তু দর্শক সেই তুলনায় অনেক কম বাড়ছে। নাটক এখন টিভি সিরিয়াল, ওটিটি প্লাটফর্ম, ফিল্ম জগতে প্রবেশের পাদানি। কিছুদিন আগে আমাদের পাড়ায় নাট্যোৎসব উপলক্ষে আমাদের রাজ্যের এক মন্ত্রী তার বক্তব্যে ছেলেমেয়েদের নাটক করতে বলেন সিরিয়াল, সিরিজে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনার কথা বলে। তাহলে সত্যি সত্যিই কি এতো নাটকের দল, এতো নাটক, এতো নাটক করতে উৎসাহী ছেলে মেয়ে নাটক করতে আসে সব ওই উদ্দেশ্যে? ৭৫ বছর আগে যে উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন শুরু হয়েছিল এখন সেই উদ্দেশ্যটাকেই পাল্টে দেবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সবাই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন যে সম্প্রতি কিছু দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী অথচ ইতিমধ্যে পরিচিত নাটকের মানুষ এই থিয়েটারের আঙিনায় আসছেন এবং থিয়েটারকে কীভাবে আদর্শচ্যুত করে চালানো যায় সেই চেষ্টা করছেন। । উদ্দেশ্য তো সমাজ পরিবর্তনের হতে পারে না, উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত আকাঙ্খা পূরণের। আর একটা বিষয়ও সাধারণের অজ্ঞাতে থিয়েটারের অর্থনীতির সাথে জড়িয়ে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সেটা হলো সরকারি গ্রান্ট। সেই গ্রাণ্ট পাবারও শুনেছি অনেক ফন্দি ফিকির আছে। আবার সবাই যে সেই অনুদান পায় সেরকম নয় এবং পাওয়া সম্ভবও নয়। এই সময় লক্ষ্য করছি কোন নাট্যকর্মী যদি কোন সিরিয়ালে বা পর্দায় কোন এক ভূমিকায় অভিনয় করেন তাহলেই সোস্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করছেন সেটা দেখার অনুরোধ করে। বেশি দর্শক যদি সেই কাজটি দেখেন তাহলে সেই অভিনেতারও কাজের জায়গাটা পোক্ত হয়। এটাও তাদের টিকে থাকার লড়াইয়ের অঙ্গ, কোনো দোষের নয়। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মতো নাট্যকর্মী ও নাট্যদলগুলোও আত্মপ্রচারে নিমগ্ন। আমি কাউকে আঘাত দেবার জন্য এই কথাগুলো বললাম না। আমি বলতে চাইছি এসবই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি। এই ব্যবস্থাটাকে পাল্টানোর রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলন যেটা ৭৫ বছর আগে শুরু হয়েছিল সেটা এখন আর সেইরকমভাবে বজায় নেই। তবে নাট্যজগতে এখনো রাজনৈতিক আদর্শ, নিষ্ঠা, পেশাদারি দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষিত বেশ কিছু নবীন নাট্যকর্মী সংখ্যায় অল্প হলেও নাট্যআন্দোলনের লড়াইয়ের মঞ্চে রয়েছেন নাট্যমোদী দর্শকদের আশা জাগিয়ে রেখে। গ্রুপ থিয়েটার ৭৫ বছরে সমাজের বর্তমান সময়ের কলুষিত আবহের সাথে নিজেকে ভাসিয়ে না দিয়ে বামপন্থী আদর্শের জোরে থিয়েটারকে পেশাদারি দক্ষতায় সমাজ পরিবর্তনের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নিজেকে নিমজ্জিত করুক এটাই হোক এই সময়ের অঙ্গীকার।

